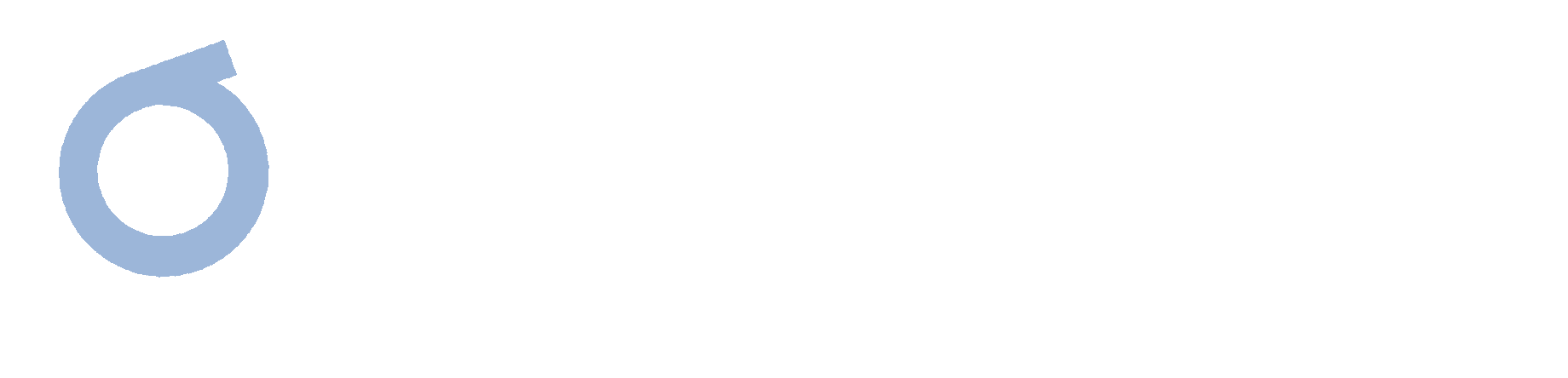‘কেউ কথা রাখেনি’,সখেদে সুনীল’দা লিখেছিলেন।তার খেই ধরে বলি, কেউ মনেও রাখেনা। অনেক বছর আগে এক সন্ধ্যায় জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে আমি জ্যোতি বসুরএকটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আমার শেষ প্রশ্নটি ছিল, ‘ভবিষ্যৎ আপনাকে কীভাবে মনে রাখবে বলে আপনি আশা করেন’? ঘোর বাস্তববাদী মুখ্যমন্ত্রী চোখের পলক পড়ার আগেই জবাব দিয়েছিলেন,” ভবিষ্যৎ কাউকে মনে রাখেনা, কাউকে নয়। ডু ইউ রিমেমবার আকবর দ্য গ্রেট?’

কথাটা ষোলো আনা সত্য, বারেবারে তার প্রমাণ পেয়েছি। আজ আবার পাচ্ছি নতুন করে। কেননা আজ আধুনিক বাংলা সাংবাদিকতার দ্রোণাচার্য, বাংলা সাহিত্যের যশস্বী কারিগর সন্তোষ কুমার ঘোষের শততম জন্মদিন। আত্মঘাতী,আত্মসর্বস্ব,ইতিহাস-বিস্মৃত বঙ্গসমাজ সেকথা ভুলে বসে আছে বেমালুম। সন্তোষবাবুর আত্মজনদের বাদ দিলে বাকি কারুর কাছে আজকের তারিখটার কোনও গুরুত্ব আছে?
আমি নিশ্চিত, সমকাল তাঁকে বিস্মৃত হলেও মহাকালের খাতায় সন্তোষ কুমার ঘোষের কীর্তির কথা লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।বাংলা সাংবাদিকতার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস যখন লেখা হবে, গবেষণার অনেকটা সময় ব্যয় করতে হবে সন্তোষ কুমারের অবদানের মূল্যায়নে, তিনিই হবেন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ভরকেন্দ্র। একইভাবে ‘ কিনু গোয়ালার গলি’ কিংবা ‘ শেষ নমস্কার- শ্রীচরণেষু মা’কে’-র মতো অবিস্মরণীয় সাহিত্য-কীর্তির স্রষ্টাকে অবজ্ঞা করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসও সম্পূর্ণ করা যাবেনা।
সাহিত্যের প্রাঙ্গনে সন্তোষ কুমার ঘোষকে যদিবা সমকক্ষের প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে পড়তেও হয়, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের আসনটি ছিনিয়ে নেবেন অবশ্যই।
সন্তোষ কুমার ঘোষ আমার বাবা সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের আবাল্য সুহৃদ ছিলেন। সেই আকৈশোর কৈশ্যে প্রথম ছেদ পড়ল সন্তোষকুমারের মৃত্যুর দিনে।সেদিন কেওড়াতলা শ্মশাণে চির-বন্ধুর মরদেহের ওপর আছড়ে পরে আমার বাবা শিশুর মতো হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। এমন নাভিতল থেকে উঠে আসা আবেগে বাবাকে এমনভাবে উদ্বেল হতে আমার মায়ের মৃত্যুর দিনটিতেও দেখিনি। দুই পুরুষের এমন নির্ভেজাল, নিষ্পাপ, নিবিড় বন্ধুত্বের দ্বিতীয় কোনও দৃষ্টান্ত আমি অন্তত আমার জীবনে দেখিনি।
ফরিদপুরের রাজবাড়ি হাইস্কুল থেকে দুই বন্ধু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন সসম্মানে, বাংলা ভাষায় দুজনেই সোনার পদক পান। সন্তোষ কুমারের ডাক নাম ছিল বাদল, বাবার ডাক নাম ছবি। ডাকনামেই তাঁরা পরস্পরকে ডাকাডাকি করতেন, সেই অভ্যেস স্বাভাবিক নিয়মে সঞ্চারিত হয়ে যায় পরবর্তী প্রজন্মেও। আমি আর আমার দিদি তাঁকে যেমন বাদল কাকা বলে ডাকি, তেমনি দোলনদি, ঝুলনদি, মিলনদি এবং টিটো আমার বাবাকে ডাকে ছবি-কাকু। বাবা আর বাদলকাকা পরস্পরের মা কে ‘ মা’ বলেই ডাকতেন। দুই মায়ের দুই সন্তান ছিলেন বাবা আর বাদলকাকা।

এই বন্ধুত্বের রসায়ন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এটা ছিল বৈপরীত্যের অমোঘ আকর্ষণ। কেননা চরিত্রে, জীবনচর্চায় দুই বন্ধু ছিলেন দুই মেরুতে। আমার পিতৃদেব ষোলো আনা মধ্যবিত্ত মাস্টারমশাই, হিসেবি, সাবধানী, কর্মজীবনের বেশিরভাগটা তাঁর কেটেছে বাংলার মফ:স্বলে। বাদলকাকা বেহিসেবী, উদ্দাম, বেপরোয়া, জেদি, একরোখা। এহেন বৈপরীত্যে বাঁধনের কাজ করেছিল নি:স্বার্থ ভালবাসা ছাড়াও আরও একটা জিনিস, তা হল বাংলা ভাষা আর বাংলা সাহিত্যের প্রতি দুই বন্ধুর নিঃশর্ত আনুগত্য। বাদলকাকা মাঝেমাঝেই আমার কাছে ক্ষেদোক্তি করতেন,” জানতো, ছবির কাছে একটি বিষয়ে আমি হার মেনেছি। ছবির মতো বাংলা গদ্য লিখতে আমি পারলামনা।” আমার মনে হত এটা বাদলকাকার স্বভাব-বিরোধী বিনয়, শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে সচেতনভাবেই কিছুটা সম্মান-জ্ঞাপন। বাড়ি ফিরে বাবাকে যখনই এ কথা বলতাম তাঁর চোখ-মুখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আহ্লাদে আটখানা দেখাত অমন গম্ভীর মানুষটিকেও। আমি বুঝতে পারতাম বাবার কাছে বন্ধুর এই স্বীকৃতির তাৎপর্য কতখানি।
বাবার বাংলা গদ্যের অনুরক্ত পৃষ্ঠোপোষক বাদলকাকা ছিলেন আমার মা কল্যাণীর রবি-গানের সবচেয়ে ভারী ওজনের শ্রোতা ও অনুরাগী। বাবা যখন যেখানে অধ্যাপনা করেছেন, গাড়ি হাঁকিয়ে সেখানেই আসতেন বাদলকাকা। এলে দিন কতক থেকেও যেতেন। বাবা বন্ধুকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকত, তা দেখে আমার দুষ্টুমিপনা কয়েকগুণ বেড়ে যেত। সন্তোষ কুমার ঘোষের দৌলতে পাড়া পড়শির কাছে সাময়িকভাবে হলেও আমাদের নম্বর কিছুটা বাড়ত। তাঁর গাড়িতে চড়ে এদিক- সেদিক বেড়াতে যাওয়ার সুযোগটা ছিল উপরি-পাওনা। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীল এইভাবে একবার বাদল কাকার সঙ্গে আমরা পলাশিতে গিয়েছিলাম। পলাশির প্রান্তরে সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর গোল হয়ে বসে আমরা সবাই একমনে মায়ের গান শুনছিলাম। মাথার ওপরে শুক্লপক্ষের চাঁদ, প্রায় মায়াবী পরিবেশ, মা গাইতে শুরু করলেন, “ ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে তুমি আমায়।” মায়ের গানশুনে প্রায় বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বাদলকাকা। কলকাতায় ফিরে এসে একবার তিনি কথায় কথায় কনিকা বন্দোপাধ্যায়কে বলেছিলেন,” ছুটির নিমন্ত্রণে গানটা তুমিও কল্যাণীর মতো গাইতে পারবেনা কোনও দিন।” কীভাবে জানিনা, কথাটা একসময় মায়ের কানে এসে পৌঁছলে তার কান দুটো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল। বাদলকাকা সত্যিই মনে করতেন কল্যাণীর প্রতিভা সুচিত্রা-কণিকার সমগোত্রীয়। মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে পরের দিন পাশের ফ্ল্যাটের ফোনে ফোন করে বাদলকাকা আমাকে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন,” সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল কল্যাণীর অবিস্মরণীয় প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগই পেলনা।” কেন পায়নি বাদলকাকা নির্ঘাৎ তা বুঝতেন। হৃদয় খুঁড়ে আজ এতদিন পরে বেদনা জাগানোর কোনও অর্থ হয়না, আমি তাই আর সে প্রসঙ্গে যাচ্ছিনা।
বাকি রইল আমার সঙ্গে বাদলকাকার সম্পর্ক। আমার ইংরেজি আত্মজীবনীতে ( মাই ডেট উইথ হিস্ট্রি, প্রকাশক রূপা) আমি এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছি, আর তার পুনরাবৃত্তি করছিনা। শুধু এইটুকু বলছি বন্ধু-পুত্র থেকে একদিন আমি তাঁর সহকর্মীর অবস্থানে উঠে এসেছিলাম, আশির দশকের গোড়ায়। আমার শিক্ষানবিশির প্রথম ছযটি মাস আমি তাঁর অধীনে কেবল কর্মরত ছিলাম না, আক্ষরিক অর্থেই তাঁর ছায়াসঙ্গী ছিলাম। চাকরিতে আমাকে স্থায়ী করার সুপারিশপত্রটি সন্তোষ কুমারই লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, “ আমার দীর্ঘ চার দশকের সাংবাদিক জীবনে আমি যত তরুণ শিক্ষানবিশ দেখেছি তার মধ্যে সুমন সবচেয়ে প্রতিভাবান, সবথেকে সম্ভাবনাময়।”
নয় নয় করে আজ আমিও সেদিনের বাদলকাকার মতো চার দশকের অভিজ্ঞ সাংবাদিক। একটুও অতিরঞ্জন করছিনা, বাদলকাকার ওই সুপারিশ পত্রটিই আমার পেশা জীবনের সেরা পুরস্কার।
সন্তোষ কুমার ঘোষ কেবল আমার আত্মজনের চেয়েও আপন মানুষ ছিলেননা, তিনি আমার গুরু, আমার জীবনের সবচেয়ে ঊজ্জ্বল আর রঙিন আলোক-বর্তিকা। আজ তাঁর শততম জন্মদিনে গুরু-মারা বিদ্যে ধার করে ঠিক সেই কথাটা বলি যেটা তিনি শেষ নমস্কারের উৎসর্গপত্রে তাঁর পরমগুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে লিখেছিলেন।
প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।
বাদল কাকা, আমার শত কোটি প্রণাম গ্রহন করবেন।