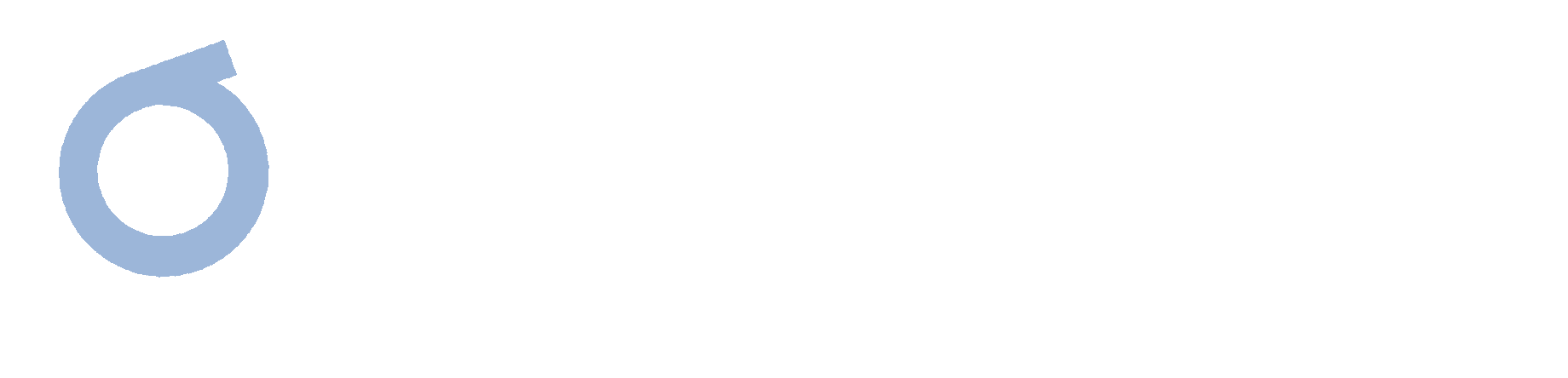সুকুমার মিত্র, এইকাল নিউজ:

এম. এ. জব্বার জন্মেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাঝেরআইট গ্রামে। দিনটা ১৪ নভেম্বর, ১৯২১। মাঝে মাত্র কয়েটা দিন পরই তাঁর জন্মশতবর্ষ শুরু হচ্ছে। এম. এ জব্বারের প্রসঙ্গ এলেই চোখে ভেসে ওঠে টানটান মানসিকতার এক খাঁটি সংগ্রামী বাঙালির অবয়ব। তাঁর জীবনের দুটি পর্যায় লক্ষণীয় একটি হল রাজনৈতিক অপরটি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বকে ঘিরে। স্থানীয় মানুষের কাছে জব্বার মিঞা, বড় ভাই, কমরেড জব্বার, ও জব্বার সাহেব এইভাবে তিনি আদৃত হতেন। ১৯৩৬ সালের শেষে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। রাইফেল চালানোর কৃতিত্বের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করলে স্বাধীনতা প্রেমী এম. এ. জব্বার তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর চাকরি ছেড়ে চলে আসেন ও কৃষক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৮ সালে কৃষি ও কৃষকের সমস্যা নিয়ে গঠিত ফ্লাউড কমিশনের তদন্তকালে তিনি রাজধানী দিল্লিতে যান। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক সভার গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। এরপর পার্টির সাংগঠনিক নানা কাজ ও আন্দোলনে সর্বক্ষণের জন্য যুক্ত হয়ে পড়েন। দেশে তখন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ। ত্রাণের কাজে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপরই এশিয়ার বৃহত্তম মেছোঘেরি বা জলকর গোবেড়িয়ার মেছোঘেরির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। গোবেড়িয়ায় কৃষিজমিতে নোনাজলের ঘেরি বানানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে বসিরহাট মহকুমা সহ বৃহত্তর সুন্দরবন এলাকায় সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তার করে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার কাজকে তিনি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। গোবেড়িয়া মেছোঘেরি আন্দোলনকে দমন করতে স্থানীয় জমিদার ও জোতদারদের ষড়যন্ত্রে জব্বার সাহেব এক বছর কারাবাস করেন।১৯৪৬ সালে সারা দেশে যখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চারে শান্তি, সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানালে আবারও কারাবাস করতে হয়। তখন গোটা বাংলায় কৃষক তেভাগার দাবিতে আন্দোলনে সোচ্চার। কারাবাসে থেকে তিনি এলাকায় তেভাগা আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হলে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে তিনিও মুক্তি পেয়ে পার্টির কাজে আরও বেশি করে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৮ সালে জোতদাররা এক গভীর চক্রান্ত করে তাঁর বাসগৃহে আগুন ধরিয়ে দেয়। তবু তিনি তাঁর পথ ও মত থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি জনসেবামূলক নানা কাজে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। হাড়োয়ায় রাস্তাঘাট, হাসপাতাল তৈরিতে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। এই সব আন্দোলনের জন্য তাঁকে নানা নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। সেই নিপীড়নের প্রভাব পড়েছে গোটা পরিবারের উপর। স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারে তাঁর জন্ম। নিজেও ইংরেজ সামরিক বাহিনীর চাকরি ছেড়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিলেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে মাসিক ভাতা গ্রহণ করেননি। ১৯৬০ সালে লেবুতলা, মুনশিঘেরি, রামজয়ঘেরির বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের নেতা এম. এ. জব্বার। জোতদারদের চক্রান্তে চলে পুলিশি নির্যাতন ও হেনস্থা। ১৮০ জন কৃষক সহ তিনি ফের গ্রেপ্তার হন। প্রায় দুই বছর কারাবাস করেন। ১৯৬২ সালে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে গোবেড়িয়ার জমিদারের চক্রান্তে আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁকে পাকিস্তানের গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে ভারতরক্ষা আইনে তিনি ফের গ্রেপ্তার হন। ১৯৬৫ সালে মুক্তি লাভ করার পর রানিগাছি রিক্রিয়েশন বাঁধ, হাড়োয়া নাসিরহাটি পাকা সড়কের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই আন্দোলনের ফলে সরকার সেই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। সিপিআই-এর অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা কমিটির তিনি সদস্য ছিলনে। কৃষক সভার জেলা কমিটির সহ সভাপতি ও রাজ্য কৃষক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি হারান। তারপরও টানা আট বছর সিপিআই-এর হাড়োয়া আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সিপিআই-এর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি সদস্য হিসেবেও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৫ সাল নাগাদ পার্টির সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে মত বিরোধের জন্য সক্রিয় দলীয় রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও আজীবন তিনি মার্কসবাদী হিসেবে নিজেকে মনে করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ছিল মারাত্মক দুর্বলতা। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের প্রতি ছিলেন আস্থাশীল। সিপিআই ও কৃষক সভার নানা কাজে যুক্ত থাকার পাশাপাশি স্থানিক ইতিহাস চর্চা ও প্রচারে এম. এ. জব্বার আত্মনিয়োগ করেছিলেন। হাড়োয়া, চন্দ্রকেতুগড়, খাসবালান্দা এলাকা থেকে প্রাপ্ত পুরাসামগ্রী নিয়ে নিজ বাসভবনে গড়ে তোলেন বালান্দা প্রত্ন সংগ্রহশালা। প্রাচীন বাংলার অতীত ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, দেশ-বিদেশের ইতিহাস জানার অদম্য আগ্রহ ছিল স্বশিক্ষিগত এই মানুষটির। কিন্তু নিজের অদম্য আগ্রহে তিনি জ্ঞানের আধার হয়ে উঠেছিলেন। তিনি সব সময়ে বলতেন ঐতিহাসিকরা যাই লিখে থাকুন না কেন তা যুক্তি, তর্ক ও তথ্যের নিরিখে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতে হবে। নিজের মত আবার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ছুটে যেতেন বিভিন্ন প্রান্তে। জ্ঞান আহরণের জন্য সুন্দরবনের এই মানুষটি আশ্রয় নিতেন ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, ধর্মগ্রন্থের। মাটির নীচ থেকে উদ্ধার হওয়া প্রত্ন সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। নিছকই পোষাকি ইতিহাস গবেষণায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে কাজ করার তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না। জব্বার সাহেব মনে করতেন, হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা মৌজায় অবস্থিত লাল মসজিদ আসলে একটি বৌদ্ধ মহাবিহার। আর বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড় এলাকা হচ্ছে প্রাচীন ‘গাঙ্গে বন্দর’। এই মত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নানা তথ্য ও তত্ত্ব আবিস্কারে নিরলস পরিশ্রম করে গিয়েছেন। পির গোরাচাঁদ, গোরাইগাজি, চন্দ্রকেতুগড়, খনা-মিহিরের ঢিবি, লালমসজিদ ইত্যাদিকে সঙ্গে রেখেই পার্শ্ববর্তী নানা অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে ও প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে পথিকৃৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। হাড়োয়া সংলগ্ন চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নক্ষেত্রের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে তা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে স্থানীয় সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য শুধু সংগ্রহশালা তৈরি নয়, সেই সংগ্রহশালায় সাধারণ মেঠো মানুষের দ্বার ছিল অবারিত। তিনি মনে করতেন আঞ্চলিক ইতিহাস রক্ষার বোধ ও দায়িত্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারলেই দেশের সার্বিক ইতিহাস প্রণয়নের কাজ সুদৃঢ় হবে। এই লক্ষেুই তিনি গঠন করেছিলেন চব্বিশ পরগনা সংগ্রহশালা ও ইতিহাস সমন্বয় সমিতি। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সেই সংগঠনের আহ্বায়ক।১৯৮৮ সালের ২৭ জুলাই মাত্র ৬৭ বছর বয়সে হাড়োয়ায় নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। হাড়োয়ায় তাঁর বসতবাড়ির গা ঘেষে বয়ে চলা বিদ্যাধরী নদীতে মিলেছে নানা প্রত্ন দ্রব্য। তাঁর সংগ্রহশালায় রাখা মানুষের নিম্ন চোয়ালের প্রস্তুরীভূত পাঁচটি দাঁত দেখলে চমকে উঠতে হয়। রেডিও কার্বন (কার্বন-১৪) পরীক্ষাঁয় হায়দ্রাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি লিখিতভাবে জানিয়ে দেয় মানুষের প্রস্তুরীভূত ওই দাঁতের বয়স দশ হাজার বছরের বেশি। জব্বার সাহেব-এর দাবি, হাড়োয়ায় ছিল প্রাচীন নদী বন্দর। গ্রিস, রোম প্রভৃতি দেশ ও পশ্চিম ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তার বহু প্রমাণ নদীবক্ষ হতে প্রাপ্ত পুরাসামগ্রী। যা কিনা তাঁর সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার পাশাপাশি তা সংরক্ষণের জন্য জব্বার সাহেব সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে সিপিআই সাংসদ রেণু চক্রবর্তী সংসদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চন্দ্রকেতুগড় ও লালমসজিদ সংরক্ষণে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানান। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলক খননকার্য হয় চন্দ্রকেতুগড় ও খনা মিহিরের ঢিবিতে। সেই খননের সময় ও তার পর নানা সময়ে প্রাপ্ত এই এলাকার পুরাবস্তু আশুতোষ সংগ্রহশালা, রাজ্য প্রত্নশালা, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে স্থান পেয়েছে। বেড়াচাঁপায় সম্প্রতি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দিলীপ মৈতের ব্যাক্তিগত সংগ্রহ নিয়ে তৈরি হয়েছে চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা। হাড়োয়ায় অনুরূপ উদ্যোগে বালান্দা প্রত্ন সংগ্রহশালাটিকে সাইট মিউজিয়াম হিসাবে রাজ্য সরকার ঘোষণা করুক এমনটা জব্বার সাহেবের আশা ছিল। বেড়াচাঁপায় রাজ্য সরকারের চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালায় এম.এ.জব্বারের সংগৃহীত কিছু পুরাসামগ্রী নিয়ে তাঁর নামে একটি গ্যালারি হোক এমন আশা করেন স্থানীয় ইতিহাসপ্রেমী মানুষেরা। স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের উপর জব্বার সাহেবের সবকটি পুস্তিকা ও গ্রন্থগুলি তিন দশক আগেই নিঃশেষিত। সম্প্রতি গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ-এর উদ্যোগে সবকটি গ্রন্থকে এক সঙ্গে সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন তহমীনা খাতুন ও দীপককুমার দাঁ। প্রবাদপ্রতীম এই মানুষটি আর কয়েক দিন পরেই শতবর্ষে পা রাখবেন। জন্মশতবর্ষে এম. এ. জব্বার এই বাংলায় আজ বিস্মৃতপ্রায়। কমিউনিস্ট আন্দোলন বা আঞ্চলিক ইতিহাসপ্রেমীদের আলোচনায় এই মানুষটির বহুমুখী কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন থাকলেও তার কোনও উদ্যোগ নেই। এটাই আক্ষেপের।