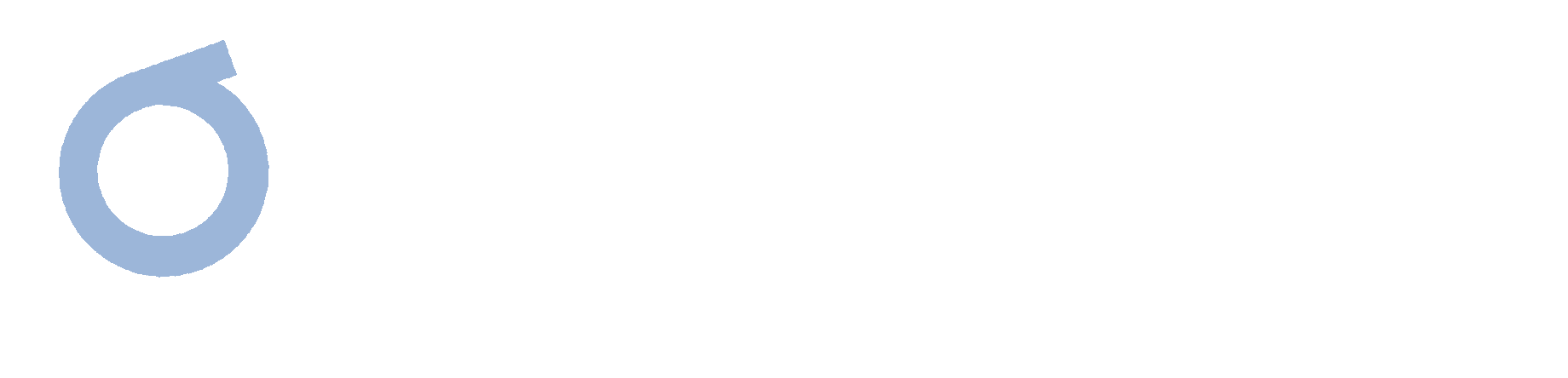|| ফেরা ||

ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘর ছুঁই ছুঁই এমন অবস্থায় জয়িতার মোবাইলে ফোনটা এলো। ফোনটা বাজছে। অথচ ফোনটা ধরার জন্য জয়িতা কোনরকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ও খুব ভালো করেই জানে ফোনটা কে করেছে। এই নিয়ে সারাদিনে অন্তত দশবার ফোন করে ফেলেছে নিলয়। একটা মানুষ কতখানি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকলে দিনের মধ্যে এতবার ফোন করতে পারে? “কী করছো? আসছো তো? এখন কোথায়?” ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। জয়িতা বিরক্ত হচ্ছে। আরে বাবা, হ্যাঁ, কথা তো হয়েই রয়েছে। যাবো বলেছি যখন তখন যাবোই। আশ্চর্য! এত ঘনঘন ফোন করার কী আছে? ছেলেরা নিজেদের ভাবেটা কী? ঘনঘন সিদ্ধান্ত পাল্টানো ওদের স্বভাব। মেয়েদের নয়। ছেলেরা সাধারণত অস্থির মস্তিষ্কের হয়। মেয়েরা তা নয়। কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে তাদের হাজারবার আগে পিছে চিন্তা করতে হয়। পুরুষ মানুষদের সেসব বালাই নেই। ওরা দুম করে ডিসিশন নিতেও পারে, আবার মনঃপুত না হলে বদলাতেও পারে। নিলয়ের অবশ্য দোষ নেই। আসলে বিষয়টাই এমন গোলমেলে যে ও বোধহয় এখনও ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত কিছু পরিকল্পনামাফিক শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন শান্তি নেই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ মসৃণভাবে শুরু হয়েও একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে ডুবিয়েছে। অনেকটা সেই তীরে এসে তরী ডুবে যাওয়ার মতো ব্যাপার। সুতরাং সাবধানের মার নেই। একটু বাড়তি সচেতনতা অবলম্বন করলে দোষটা কোথায়? এটা হয়ত সেই বাড়তি সচেতনতা। যার জন্য এত কিছু, তাকে কিছুক্ষণ বাদে বাদে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, মনে আছে তো দু’জনার মধ্যে কী কথা হয়েছে?
বাড়ি থেকে বেরনোর আগের মুহূর্তে জয়িতা একবার শোবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল। না, এখনও বাবিন খাটের উপর কোলবালিশখানা জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। ওর শোবার ভঙ্গি খুব বাজে। এতটুকু ছেলে হাত-পা ছড়িয়ে পুরো খাটটা একার হলেই ভালো হয়। একদম ওর বাপের স্বভাব পেয়েছে। সুজয়েরও শোওয়া ভালো না। হঠাৎ করে সুজয়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় জয়িতার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। এইসময় ওর কথা মনে করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শুধু বাবিনটার জন্য খারাপ লাগছে। ছেলেটা ঘুম থেকে জেগে উঠে মাকে দেখতে পাবে না। হয়ত খুব কান্নাকাটি করবে। সেটাই স্বাভাবিক। জয়িতা অনেকবার ভেবেছে বাবিনের উদ্দেশ্যে কিছু একটা লিখে রেখে যাবে। বাবিনের এখনও বোঝার বয়স হয়নি। সে যখন বড় হয়ে বুঝতে শিখবে, তখন পড়বে। ছোট থেকে মায়ের সম্পর্কে তৈরী হওয়া বাজে ধারণাটা তখন আর থাকবে না। অনেক সিনেমায় দেখা যায় না, মা খুব ছোটকালে পরিস্থিতির চাপে সন্তান ফেলে চলে যায়। বাড়ির বড়রা তাদের অনেক মনগড়া গল্প শোনায়। তার মা মোটেই একজন ভালো মহিলা ছিল না। জীবনে তার যত সমস্যাই থাকুক, সন্তানকে কেউ এভাবে ফেলে রেখে যায়? মা ছিল খুব স্বার্থপর। শুধু নিজের সুখের কথা ভেবেছে। তখন থেকেই সন্তানের মনের মধ্যে মা সম্পর্কে বাজে ধারণা জন্মাতে শুরু করে। মাকে সে ঘৃণা করতে শুরু করে। তারপর একদিন পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে মায়ের লেখা চিঠি হাতে পড়ে যায়। চিঠিতে মা লিখে রেখে গেছে, কী পরিমাণ দুঃখ জ্বালায় জীবন তার দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, যে কারণে সে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। জয়িতাও ভেবেছে এমনি কিছু একটা সে লিখে রেখে যাবে। তবে চিঠি সে লিখবে না। চিঠি বড্ড ছোটখাটো জিনিস। কোথাও হারিয়ে যেতে পারে। চিঠি না, সে লিখবে ডায়েরি। যার মধ্যে সুন্দর সুন্দর শব্দে বাবিনের মায়ের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা লেখা থাকবে। লেখাটার একটা সুন্দর নাম থাকবে। কী নাম দেওয়া যায় এটা নিয়ে অনেক ভেবেছে জয়িতা। কিন্তু মুশকিলটা হলো, এখনও পর্যন্ত একটাও ভালো নাম সে ঠিক করে উঠতে পারেনি। মোড়ের মাথার ‘পেপার হাউজ’ থেকে একটা ছোট্ট অথচ সুন্দর ডায়েরি কিনে এনেছে জয়িতা। সঙ্গে একখানা দামী কলম। ছেলের জন্য মায়ের দুঃখের ইতিহাস লিখে রেখে যাবে, সবকিছু ভাল না হলে চলে? জয়িতার ডায়েরি লেখার অভ্যাস নেই। কী লিখবে? কীভাবে লেখা শুরু করবে? ভেবে ভেবে মাথা নষ্ট হবার যোগাড়। এমনি সময় কত কথা মনে পড়ে। লিখতে বসলে মাথা পুরো ফাঁকা, কোন কথাই আর মনে আসে না। এ তো মহা সমস্যা। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেছে। ছেলের জন্য শেষপর্যন্ত কিছু আর লেখা হয়ে ওঠেনি। ছেলে মাকে জানতে পারবে না। মা একজন বাজে মহিলা, এই ধারনা নিয়ে ছেলেটা বড় হবে।
জয়িতা আর দাঁড়ালো না। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা অর্থহীন। শুধু বাজে সময় নষ্ট।
বারান্দা ক্রস করে আসার সময় রবির-মা’র সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। চেয়ারে বসে এতক্ষণ ঝিমোচ্ছিল। পায়ের শব্দে চোখ খুলে তাকালো—”কোথাও বেরুচ্ছো বউদিমণি?”
জয়িতা কী বলবে ভেবে পেল না। রবির-মা এ-বাড়ির কাজের মাসি। তার সামনে এমন অপ্রস্তুত হবার কোন কারণ নেই। তবুও জয়িতার মনে হলো, একটু ওদিক হলে ধরা পড়ে যেতে পারে। আবার কিছু একটা না বলাটাও চরম অভদ্রতা হবে। রবির-মা’র কথার উত্তর না দিয়ে জয়িতা পাল্টা প্রশ্ন করল, “কেন?”
—”কিছু না। আসলে ছ’টার সময় আমি একটু বেরুতাম।”
অন্যসময় হলে জয়িতা জিজ্ঞেস করত, “কোথায় যাবে? তোমার ভাইয়ের বাড়ি?” ঘূর্ণিতে রবির-মায়ের ভাইয়ের বাড়ি। মাঝে মাঝে সেখানে যায় সে। আজও হয়ত সেখানেই যাবে। কিন্তু জয়িতা তেমন কিছু বলল না। শুধু মনে মনে বলল,বেছে বেছে আজকের দিনটাতেই তোমার ভাইয়ের বাড়ি যাবার কথা মনে হলো? বারান্দা থেকে নেমে আসতে আসতে জয়িতা বলল,”ততক্ষণে তোমার দাদাবাবু চলে আসবে।” কথাটা বলল বটে, কিন্তু জয়িতা জানে কথাটা সে ঠিক বলল না। সুজয় কোনদিনই এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না। আজও সেই রুটিনের খুব একটা হেরফের হবে বলে মনে হয় না। এটা জয়িতার থেকে ভালো তো আর কেউ জানে না। সুজয়ের এখন বাড়ি ফেরার কোন প্রশ্নই নেই। ইদানিং তার বাড়ি ফেরার ব্যপারে আগ্রহ কম। নেহাত বাড়িতে বাবিন আছে, তাই না ফিরে উপায় নেই। সুজয়ের কাছে জয়িতার হয়ত কানাকড়িও দাম নেই, কিন্তু বাবিনকে অবহেলা করা ওর পক্ষে অসম্ভব। কে যেন বলেছিল, জগতে খারাপ স্বামী খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু খারাপ বাবা বোধহয় খুব কমই আছে।
রাস্তায় নেমে কোনদিকে তাকালো না জয়িতা। হনহন করে বাসস্টপের দিকে এগিয়ে চলল। সে চাইছে না কেউ তাকে দেখে ফেলুক। সাবধানের মার নেই। একবার মনে হলো, মোবাইলটায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয় ক’টা বাজল। বিকেলের দিককার গাড়ি। চারটে ছাব্বিশে ছাড়ার টাইম। নিলয় না বললেও জয়িতার ট্রেনের টাইমটা জানাই ছিল। কেন না এই ট্রেনটাতে চড়ে ও বহুবার নৈহাটি গেছে। নৈহাটিতে ওর বাবার বাড়ি। বাবা অবশ্য বেঁচে নেই। তবে মা আছে। মায়ের খোঁজ খবর নিতে যাওয়া লাগে। কিন্তু এবারের ব্যপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। এই যাওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটা ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র গন্ধ আছে। একটা অনিচ্ছাকৃত গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হচ্ছে। জয়িতাকে, নিলয়কে দু’জনকেই। সারা দুনিয়ার মানুষ মনে হয় কাজকর্ম বাদ দিয়ে শকুনের দৃষ্টিতে ওঁৎ পেতে বসে আছে। জয়িতা এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছে? কেন যাচ্ছে? মোবাইলটা হাত-ব্যাগের মধ্যে আছে। ইচ্ছে করলেই মোবাইলটা বের করে সময়টা দেখে নেওয়া যায়, কিন্তু জয়িতা তেমন কিছু করল না। ভাবল, থাক, সময় দেখে আর কাজ নেই।
বাস স্টপে এসে পৌঁছতে প্রায় মিনিট সাতেক লেগে গেল। জয়িতা এর আগে কখনও বাড়ি থেকে এমনি করে হেঁটে হেঁটে বাস স্টপে এসেছে কি-না ঠিক মনে করতে পারল না। রিক্সা অথবা আজকাল টোটোর চল হয়েছে তাতে। আজ একেতেই হাতে সময় কম রিক্সা কিংবা টোটো ফোটো করে এলেই ভাল হতো। অন্য সময় এখান দিয়ে কত ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু দরকারের সময় একটাও চোখে পড়ল না। অপেক্ষা করতেও ইচ্ছে করল না। পাছে দেরি হয়ে যায়। জয়িতা চাইছে না কোনভাবে এতটুকু সময় নষ্ট হোক।
বাস স্টপে দু-চারজন আগে থেকেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। জয়িতা এদের কাউকে চেনে না।
ডিসেম্বরের উত্তুরে হাওয়ার শিরশিরানির মধ্যেও জয়িতা মনে হলো রীতিমত ঘেমে-নেয়ে উঠেছে। রুমাল দিয়ে মুখটা-গলার কাছটা একটু বাদে বাদেই মুছে যাচ্ছে। টেনশনে মানুষ নার্ভ ফেল করে শুনেছে। তবে কি জয়িতা টেনশন ফিল করছে? অস্বীকার করার উপায় নেই, তা একটু হচ্ছে বৈকি। জীবনে এই প্রথমবারের জন্য এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ সে করতে চলেছে, টেনশন তো কিছুটা হবেই। অবশ্য যে কোন বড় ধরনের দুঃসাহসিক কাজ মানুষ প্রথমবারের জন্য করে। তারপরেও করে। কিন্তু প্রথমবারের উত্তেজনা পরেরগুলোতে থাকে না।
নিলয়ের সাথে দেখা না হলে জয়িতা ভাবতেও পারত না জীবনের এই পর্যায়ে পৌঁছেও নতুন করে আরেকটা জীবন শুরু করা যায়। একটা সময় ও হাল ছেড়ে দিয়েছিল। যে দমবন্ধ করা অবস্থার মধ্যে ও আটকে পড়েছে, এখান থেকে বেরনো ওর পক্ষে কার্যত অসম্ভব। দিনের পর দিন এভাবে থাকতে থাকতে শ্বাসরোধ হয়ে একদিন নির্ঘাত মারা পড়বে। কী-ইবা বয়স ওর। তিরিশ কি হয়েছে? না, না অত হবে না। বড়জোর সাতাশ কি তার চেয়ে সামান্য বেশি। ওর সমবয়সী বন্ধুবান্ধবরা এখনও দিব্বি পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ চাকরি বাকরি নিয়ে যাকে বলে ওয়েল সেটেলড। শুধু জয়িতার অবস্থাই খুব একটা ভালো না। অল্প বয়সে বিয়ে টিয়ে করে, বাচ্চাকাচ্চা হয়ে একেবারে যা তা অবস্থা। ওর এই অবস্থার জন্য কেউ দায়ী না। দায়ী ও নিজে। অন্যান্য বাড়িতে যেমন মেয়ে একটু হাতেপায়ে বাড়বৃদ্ধি হলেই বাড়ির লোকজন বিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ওর বেলায় সেরকম কিছু হয়নি। বাড়ি থেকে কখনও বিয়ে করার জন্য ঠেলাঠেলি করেনি। না বাবা করেছে, না দাদারা। আত্মীয়-স্বজনরা অবশ্য দু-একবার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল— এই বেলা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতি বোঝা বড় দায়। যা দিনকাল পড়েছে কোথা থেকে কী হয়ে যায় আগেভাগে বলা মুশকিল। জয়িতার বাবা এসব কথায় কখনই খুব একটা আমল দেননি। উল্টে তিনি সেইসব হিতৈষী আত্মীয়-স্বজনদের পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, মেয়ে আমার লক্ষ্মী মা। ওর জন্মের পর থেকেই আমার যা কিছু আয় উন্নতি হয়েছে। ওকে পরের বাড়িতে পাঠানো নিয়ে আমি কোন তাড়াহুড়ো করার পক্ষপাতি না। ওর উপর আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। তা, বাবার ভরসার দাম খুব দিয়েছে জয়িতা। সুজয়কে যে ওদের বাড়ির সবাই খুব পছন্দ করে সেটা বলা যাচ্ছে না, আবার খুব যে খারাপ চোখে দেখে তাও না। সুজয় এমনি যেমন যাই হোক, জয়িতার বাবা-মা বা দাদা-দিদিদের যথেষ্ট সম্মান করে। স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে ওর ব্যবহার, কথাবার্তায় আন্তরিকতার অভাব কখনও চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। সুজয় জয়িতার থেকে বয়সে প্রায় কুড়ি বছরের বড়। মাথার চুল অর্ধেকের বেশী সাদা। বাইরে থেকে অবশ্য বোঝার উপায় নেই। নিয়মিত চুলে কলপ করে। মাথায় যে ক’গাছা চুল এখনও অবশিষ্ট আছে তারা প্রত্যেকেই কালো এবং কুচকুচে কালো। প্রফেসর মানুষ। একটু গুরুগম্ভীর ভাব আছেই। অবশ্য প্রফেসর মানেই যে এমন ভারিক্কি মেজাজের হতে হবে তার কোন মানে নেই। জয়িতার চেনাজানার মধ্যে এমন বেশ কয়েকজন প্রফেসর আছেন যাদের দেখলে মনে হয়, বয়সটা তাদের জন্য একটা সংখ্যা মাত্র। প্রকৃতির নিয়মে তাদের শরীরের বয়স হয়ত বেড়েছে, মনের বয়স সেভাবে বেড়েছে বলে মনে হয় না। সবসময় যেন টগবগ করে ফুটছে। ছাত্রীদের সাথে এমন ফ্লার্ট করে যে দেখে মনেই হয় না, যৌবনের সেই সোনালী দিনগুলো তাঁরা অনেকদিন আগেই পিছনে ফেলে এসেছেন । জয়িতার বাবা অবশ্য মেয়ের পছন্দকে অস্বীকার করেননি। তিনি শুধু বলেছিলেন,”তুমি যখন পছন্দ করেছো, তখন ভালো বুঝেই করেছ। তুমি সুখী হলেই আমি খুশি।”
সুজয়কে বিয়ে করে জয়িতা বোধহয় সবাইকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিতে চেয়েছিল। দেখো, আমার পছন্দ। সবার থেকে নিজেকে ডিফরেন্ট প্রমাণ করার এই প্রচেষ্টা কতখানি কাজে এসেছে, জয়িতা অবশ্য এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। বিয়ের দু’বছরের মাথায় বাবিন হলো। জয়িতার দায়িত্ব এক ঝটকায় অনেকটাই বেড়ে গেল। সুজয়ের বউ থেকে বাবিনের মা। একটা ছোটখাটো জার্নি। জয়িতার তো বেশ খুশি হবার কথা। সেটা হচ্ছে না, তার বদলে বিরক্ত লাগছে। বিরক্ত লাগছে সুজয়কে দেখে। সুজয়ের দায়িত্ববোধ নিয়ে কোনো কথা হবে না। ওর কর্তব্যবোধ খুব প্রখর। ও খুব ভালো করেই জানে জয়িতার বাড়ির লোকেরা ওকে খুব একটা পছন্দ করে না। তথাপি এসব নিয়ে ওর কোন অভিযোগ নেই। জয়িতা ইচ্ছে করে ওর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে, ব্যপারটা যেন সে গায়েই মাখছে না। ওর এ-জাতীয় ভাল মানুষী ভাবভঙ্গি জয়িতার সহ্য হচ্ছে না। জয়িতা মনে মনে ‘ঢ্যামনা ব্যাটাছেলে’ বলে নাগাড়ে গাল দিচ্ছে। কোনকিছুতেই ওর কোন হেলদোল নেই। বিষয়টাকে সে খুব স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে। বাবিন হবার পর সুজয়ের সেই কর্তব্যবোধটা আরো বেড়েছে। ছেলেকে নিয়ে ওর অনেক স্বপ্ন। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে, ছেলে ছেলে করে অস্থির। জয়িতার মাঝে মাঝে মনে হয়, সুজয়ের কাছে ওর গুরুত্ব আগের তুলনায় অনেকটাই কমে গেছে।
নিলয়ের সঙ্গে জয়িতার আলাপ খুব বেশিদিনের না। বড়জোর বছরখানেক হবে। দু-এক মাস এদিক ওদিকও হতে পারে। সমিতির কাজে মাঝেমধ্যেই জয়িতাকে কৃষ্ণনগর ব্যাঙ্ক অফ বারোদা ব্রাঞ্চে যেতে হয়। ওখানেই নিলয়কে প্রথম দেখে জয়িতা। খুব বেশি বয়স না। জয়িতার সমবয়সী অথবা জয়িতার থেকে দু-এক বছরের ছোটই হবে বোধহয়। এত কম বয়সে কী অসাধারণ দক্ষতার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলাচ্ছে ভাবাই যায় না। ব্যাংকের যাবতীয় চাপ মনে হয় ও একাই নিয়ে বসে আছে। ওর টেবিলের সামনে প্রায় সময়ই একটা ছোটখাটো ভিড় লেগেই থাকে। গ্রাহকদের বিবিধ সমস্যায় ওর প্রায় নাজেহাল অবস্থা। তবুও মুখে কোন বিরক্তির ছাপ নেই। জয়িতার যেটা সবথেকে ভাল লেগেছে, সেটা হলো ওর মুখের অমায়িক হাসি। ওর হাসির মধ্যে একধরনের শিশুর সারল্য আছে। দেখলেই মনটা অটোমেটিক ভাল হয়ে যায়।
সুজয় নিলয়কে কখনও দেখেনি। সুতরাং চেনার কথা না। নিলয়ের সঙ্গে জয়িতার মেলামেশার কথা সে কিছু জানে বলে মনে হয় না। জানলেও অসুবিধা কিছু নেই। সুজয় যে টাইপের মানুষ, জানতে পারলে হয়ত মনের দিক থেকে প্রচণ্ড আহত হবে, কিন্তু খুব বেশি বেগড়বাই করবে বলে মনে হয় না। কেননা এতদিনে সুজয়কে যতটুকু বুঝেছে, সুজয় সেই টাইপের মানুষই না। তবুও জয়িতা চায়নি সুজয় বিষয়টা জেনে ফেলুক। ওর সামনে দিয়ে চলে যাবার মত মনের জোর জয়িতার নেই। দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা একটা থাকছেই। অতএব জয়িতা মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিল, সুজয় দিনের বেলায় বাড়ি থাকে না, নিলয়ের সঙ্গে সরে পড়ার এর থেকে ভাল সুযোগ আর হতে পারে না। কথা আছে চারটে ছাব্বিশের ডাউন কৃষ্ণনগর লোকালটা ওরা ধরে নেবে। নিলয় অবশ্য প্রাইভেট গাড়ির কথা বলেছিল। জয়িতাই না করেছে। সে চাইছে গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা স্বাভাবিকতার ছাপ থাকুক। এর মধ্যে গাড়ি-টাড়ি এসে পড়লে সমস্যা তৈরি হতে পারে। কোথা থেকে কী হয়ে যায় তার ঠিক আছে। সে যাবে ট্রেনে। কারো নজরে পড়ে গেলে যেন মনে হয় সে নৈহাটিতে বাপের বাড়ি যাচ্ছে। কোন গোলমালের সম্ভাবনা থাকবে না। কেননা এমনটা নতুন কিছু নয়, এইভাবে জয়িতা অনেকবার নৈহাটিতে গেছে। নিলয় এ-নিয়ে আর বেশি চাপাচাপি করেনি। জয়িতা যেটা ভাল মনে করবে তেমনটাই হবে। মেয়েমানুষের মন বোঝা মুশকিল। নিলয়ের এই ব্যাপারটা জয়িতার বেশ পছন্দ হয়েছে। বেশিরভাগ পুরুষদের মত নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতাটা ওর মধ্যে একেবারেই নেই। এখন এমন, পরে কী করবে সেটা অবশ্য এখনই বলা যাচ্ছে না। পুরুষরা বিয়ের আগে একরকম, বিয়ের পরে পরেই ওদের মধ্যে ‘আমার কথাই শেষ কথা’ এমন একধরনের ‘কর্তা কর্তা’ ভাব চলে আসে। বিয়ের কথা বলতেই মনে পড়ে গেল, এতক্ষণ ধরে গল্প করছি, অথচ আসল কথাটাই বলা হয়নি। প্রায় বছরদেড়েক চুটিয়ে প্রেম করার পর ওরা ঠিক করেছে, অনেক হয়েছে, আর নয়। এবার একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। সঠিক সিদ্ধান্ত মানে, এমন করে আড়ালে আবডালে মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। এই সম্পর্কের কোন নাম হয় না। এ হলো পরকীয়া। এতে একধরনের রোমাঞ্চ হয়ত আছে, তবে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মারাত্মক। এতদিনে নিলয় জয়িতার জীবনের খুঁটিনাটি অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে। জয়িতাই বলেছে। ওর যে একটা তিনবছরের বাচ্চা আছে, নিলয়কে অনেকবার সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছে। নিলয় অবশ্য বাবিনকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। জয়িতাই মানা করে দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে ও নিজেই একটা অ্যাডভেঞ্চারের ঘোরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এর শেষ পরিণতি কী হতে পারে, ওর জানা নেই। কেননা এমন পরিস্থিতি জীবনে প্রথম। যার শেষ আছে, তার শুরু থাকাটাই স্বাভাবিক। জয়িতা চায় না এই অদ্ভুত দোলাচলের মধ্যে বাবিনকে এনে ফেলতে। যে নারী স্বামী থাকতেও অন্য পুরুষের হাত ধরেছে, তার স্বামীর কথা ভাবার কথা না। তবুও সে চাইছে না, সুজয়কে একেবারে নিঃস্ব করে ফেলে রেখে যেতে। বাবিনটা কাছে থাকলে ও নিজেকে অনেকটাই সামলে নিতে পারবে। বাবিন না হয়, এটা জেনেই বড় হোক, ওর মা একটা বাজে মহিলা ছিলো। যে শুধু নিজের কথা ভেবেছে। সন্তানের কথা যার একবারের জন্যও মনে আসেনি। বিচিত্র নারীর মন। সুজয়কে ত্যাগ করার কোন স্পষ্ট কারণ জয়িতার কাছে নেই। তাকে যদি সুজয়ের খারাপ দিকগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, চট করে পাঁচটা দিক বলে ফেলতে পারবে না। সুজয় কখনও তার সঙ্গে খুব একটা খারাপ ব্যবহার করেনি। স্ত্রীকে তার মর্জি মত চলার অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। সংসারের প্রায় সবক’টা ডিসিশন জয়িতাই নেয়। তবুও সুজয়ের প্রতি জয়িতার এত রাগ কীসের? কেন তবে অন্য একজন পুরুষমানুষের হাত ধরার কথা তার মাথায় এলো? সমস্যাটা ঠিক কোথায়? তবে কি সমস্যাটা মানসিক নয়, শারীরিক কিছু? তাই যদি হবে তবে তো অন্যভাবেও বিষয়টাকে হ্যান্ডেল করা যেত। জয়িতার এক বান্ধবী মাধবী, ওর বর বিদেশে থাকে। বছরের পর বছর দু’জনার দেখা সাক্ষাৎ নেই। অথচ মাধবী নতুন নতুন বন্ধুদের নিয়ে দিব্বি আছে। কোন সমস্যা নেই। ইচ্ছে করলে জয়িতা কি পারত না, এমন বন্ধু জোগাড় করতে? অলরেডি একটি সন্তানের মা হলেও সে দেখতে শুনতে খারাপ না। আজকাল ইয়ং ছেলেরা অবিবাহিত মহিলাদের চেয়ে বিবাহিত মহিলাদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। সুতরাং ঘরে বাইরে দু’ধরনের রিলেশন রাখাটা আজকাল কোন ব্যাপারই না। এর জন্য একেবারে ঘর ছাড়ার কোন প্রয়োজন কি সত্যি সত্যিই দরকার ছিল?
আসলে জয়িতা চাচ্ছে সুজয়কে একটা সজোরে ধাক্কা দিতে। ও যে ঘুমের ঘোরে আছে, ঘুমটাকে ভাঙিয়ে দিতে।
জয়িতার যে কী হয়েছে, সুজয়কে কোনভাবেই ওর আর সহ্য হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এই নির্বিষ মানুষটার সাথে আর কিছুদিন থাকলে ও নির্ঘাত পাগল-টাগল কিছু একটা হয়ে যাবে। এখনই এখান থেকে না বেরতে পারলে যে কোন মুহুর্তে দম আটকে মারা পড়তে পারে।
অন্যদিকে নিলয়কে দেখলে মনটা হঠাৎ করে ভাল হয়ে যায়। একধরনের অদ্ভুত ভাললাগায় মনটা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। এই যে এতগুলো দিন ওর সাথে জয়িতা মেলামেশা করছে, পরস্ত্রীকে বাগে পেয়েও কখনও বাড়তি অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করেনি। চুমু-টুমু খাওয়ার চিন্তাভাবনা দূরে থাক, নিভৃতে একলা পেয়ে কখনও জড়িয়ে-টড়িয়েও ধরার চেষ্টাও করেনি। সত্যি সত্যিই যদি তেমন কিছু সে করে বসত, জয়িতা কীভাবে রিঅ্যাক্ট করত সেটা অবশ্য এখন আর বলা যাচ্ছে না। খুব সম্ভবত ‘সবুরে মেওয়া ফলে’ এই তত্ত্বে ছেলেটার বিরাট আস্থা আছে। হয়েছেও তাই। এই যে জয়িতা আজ সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে ওর জন্য ঘর থেকে বেড়িয়ে আসতে পেরেছে, এটা তো সেই তত্বকেই মান্যতা দিচ্ছে, তাই না?
না, জয়িতা একটু যেন বেশি বেশিই ভাবছে। এত ভাবাভাবির কী আছে? নিলয়ের সঙ্গে আজ কৃষ্ণনগর ছাড়ছে, ব্যস্ এটাই ফাইনাল। নিলয় সম্পর্কে জয়িতা যদ্দুর জেনেছে মানে, নিলয় যতটুকু বলেছে, নিলয়রা দুই ভাই। নিলয় বাড়ির ছোট। বাবা-মা দু’জনেই গত হয়েছেন অনেকদিন। নিলয়ের বড়ভাই প্রলয় ফ্যামিলি নিয়ে দিল্লিতে থাকে। বড় একটা এদিকে আসে টাসে না। নিলয়দের নাকতলার বাড়িটা বছরের বেশীরভাগ সময়টা প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। একজন রিটায়ার আর্মি অফিসার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া থাকেন। নিলয় এখানেই মানে, কৃষ্ণনগরেই একটা এক কামরার ঘর নিয়ে তাও বছর চারেকের উপর হলো ভাড়া থাকে। জয়িতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে সেটার আর প্রয়োজন পড়বে না। তাকে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও পোস্টিং দেওয়া হোক, এই নিয়ে উপর মহলে মেইল, চিঠি-চাপাটি যা যা করার অলরেডি সব করে বসে আছে। এখন রিলিজ অর্ডার কবে আসে কে জানে। যতদিন পর্যন্ত না আসে ততদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তবে আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়িই ট্রান্সফার অর্ডারটা তার হাতে চলে আসবে।
(২)
বাসটা সামনে এসে দাঁড়ালো। কয়েকজন নামল। তাদের নামার মধ্যে কোনরকমের তাড়াহুড়ো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। গন্তব্যে পৌঁছে গেলে যাত্রীদের মধ্যে একটা ঢিলেঢালা ভাব চলে আসে। বাসে যারা উঠবে তাদের ব্যস্ততা বেশি। দেখলে মনে হবে এদের সকলেরই ভীষণ তাড়া আছে। জয়িতার তাড়াটা একটু বেশি।
বাসটা ফাঁকাই আছে। হাতে গোনা জনাকয়েক যাত্রী। এই সময় এই রুটের বাসগুলো মোটামুটি ফাঁকাই থাকে। চারটের পর থেকে ভিড় বাড়ে। এই বাসটা মনে হয় একটু বেশিই ফাঁকা। ট্রেন হোক কিংবা বাস জয়িতা জানালার ধারের সিটটাই পছন্দ করে। সবসময় অবশ্য পছন্দ মতো সিট পাওয়া যায় না। আজ ভাগ্য ভালো। জানালার ধারে অনেকগুলো সিট ফাঁকা পড়ে আছে। এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষ খানিকটা দোলাচলে পড়ে যায়। বাছাবাছির ব্যাপারটা মাথায় চলে আসে। জয়িতা অবশ্য বাছাবাছির রাস্তায় গেল না। সামনে যেটা ফাঁকা পেল সেটাতেই বসে পড়ল। সিটে ভালো করে গুছিয়ে বসতে না বসতেই বাস ছেড়ে দিল। এই জাতীয় বাসগুলোকে সর্বদা তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। যে কারণে যাত্রীদের কোনোরকমে ঠেলেঠুলে খোলের মধ্যে গুঁজে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ। কেউ ঠিকমতো বসতে বা দাঁড়াতে পারলো কি-না তা নিয়ে এদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই। বাসটার গতি খুব বেশি না। তবে এর তর্জন গর্জন বিরাট। মনে হয় এর ইঞ্জিনে বড়সড় কোন গণ্ডগোল আছে।
বাসে চড়তে জয়িতার একদম ভালো লাগে না। বাসে উঠলেই কেমন যেন বমি বমি পায়। গা গুলোতে শুরু করে। জানালার ধরে বসলে অস্বস্তি কিছুটা কম হয়। জয়িতার মাথায় ঘোমটা দেওয়ার অভ্যাস নেই। অথচ আজ বাসে উঠেই মাথায় আঁচলটা টেনে দিয়েছে। এটা একধরনের সাবধানতা অবলম্বন। কোন প্রয়োজন নেই। তবুও জয়িতা সাবধান হচ্ছে। সাবধানের মার নেই। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। একটু চেষ্টা করলেই জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া যায়। কিন্তু জয়িতার সেটা করতে ইচ্ছে করছে না। আসুক, হাওয়া আসুক। হাওয়াটা ওর খুব একটা খারাপ লাগছে না।
জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো জয়িতা। এতদিন ধরে ও কৃষ্ণনগরে আছে, অথচ শহরটাকে সেভাবে দেখার ফুরসত হয়নি কখনও। রাস্তার দু’ধারে বিরাট বিরাট সব হাইরাইজ বিল্ডিং যেন আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা দেখাতে চাইছে। অন্য সব বড় শহরের মত পপুলেশন এক্সপ্লোশান ব্যাপাররটা এখানেও ঘটে গেছে যেন কতকটা নিরবেই। সেটাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণনগর শহরটা তো আর কম বড় নয়। নদীয়ার সদর শহর। কোর্ট কাছারি, অফিস আদালত সমস্তকিছুই এই শহরে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খুব অল্পদিনের মধ্যে শহরটা চোখে পড়ার মত ডেভলপ করেছে। পাঁচ বছর আগের কৃষ্ণনগর আর বর্তমানের কৃষ্ণনগরের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক।
হাইস্ট্রিটের মুখটায় এসে জয়িতাদের বাসটা হঠাৎ করেই একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঝাঁকুনি এতটাই তীব্র জয়িতা সীটে বসে থাকতে পারল না। সামনের সীটের পিছনদিকটায় বের হয়ে থাকা ধাতব অংশটায় ওর কপালটা ঠুকে গেল। ” আঃ!” অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল জয়িতা। ব্যাপার কী বোঝার আগেই সয়ংক্রিয়ভাবে জয়িতার ডান হাত কপাল স্পর্শ করল। যা ভেবেছে তাই— কপালের গুঁতো খাওয়া অংশটা এরই ফুলে উঠেছে।
বাসটা জ্যামে আটকা পড়েছে। এটা অবশ্য নতুন কিছু না। বড় টাউনের এই এক ফ্যাচাং কোথায় কখন গাড়ি জ্যামে আটকা পড়ে যাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। বাজে ট্রাফিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা যদি এর জন্য দায়ি হয়, মানুষের অসহিষ্ণুতাও একটা বড় কারণ। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে তত তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। একে অপরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি না। যে যেখান দিয়ে পারছে গাড়ি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বিধিনিষেধের কোনরকমের তোয়াক্কা কেউ করছে বলে মনে হয় না।
একটু ধাতস্থ হতেই আরো অনেকের মত জয়িতাও বাসের জানালা দিয়ে মাথা বের করে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। বাসের সামনে পিছনে সারি সারি প্রাইভেট কার, টোটো, রিক্সা, বাইক সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তেমাথার মোড়ে ট্রাফিক আইল্যান্ড একটা আছে বটে। যথারীতি তার একজন ট্রাফিক সার্জেন্টও আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সেই ভদ্রলোককে কাছে পিঠে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে দু-চারজন সিভিক ভলেন্টিয়ারকে দেখা যাচ্ছে। এদের তৎপরতা আবার বাড়াবাড়ি পর্যায়ের। আজকাল এদের দাপাদাপি দেখলে বিরক্তি ধরে যায়। ‘বাঁশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত’ বলে বাংলায় প্রচলিত একটা বাগধারা আছে, এদের কর্মকাণ্ড দেখে জয়িতার সেটাই মনে পড়ে যাচ্ছে। জয়িতা দেখল একজন টোটোওয়ালা সামান্য ফাঁক গলে বেরোবার চেষ্টা করতে গিয়ে সিভিক ভলেন্টিয়ারের নজরে পড়ে গেছে। সিভিক ভলেন্টিয়ার একটা অল্পবয়সী ছেলে। তার হাতে লাঠি। ছেলেটার কাজ করার প্রক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে, নিজের ডিউটি সম্পর্কে সে একটু বেশিই সচেতন। সে দৌড়ে গিয়ে এরইমধ্যে টান মেরে টোটোর চাবি খুলে নিজের জিম্মায় নিয়ে নিয়েছে। টোটোওয়ালা বেচারা কাকুতি মিনতি শুরু করে দিয়েছে। সিভিক ভলেন্টিয়ার ছেলেটি দাঁত খিঁচিয়ে তাকে কিছু একটা বলছে। বেচারা টোটোওয়ালাকে দেখাচ্ছে অনেকটা ভারত-পাকিস্তানের বর্ডার ক্রস করে ফেলা অবুঝ পাবলিকের মত। জয়িতা এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কতক্ষণে এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবে। ওর চোখেমুখে বিরক্তি ভাব ফুটে উঠেছে। এইসমস্ত হাবিজাবি কারণে অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে। এখন এই জট কতক্ষণে কাটবে বোঝা যাচ্ছে না। জয়িতার মনের মধ্যে আবার সেই অস্থিরতাটা ফিরে এসেছে। মায়ের কাছে শুনেছিল, কোন বড়ধরনের কাজ করতে গিয়ে এমন অনেক বাঁধা বিপত্তি সামনে চলে আসবে যে, মনে হবে অশুভ কোন শক্তি বিভিন্ন অছিলায় বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তখন ঘাবড়ে গেলে চলবে না। মাথাকে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নাহলে সেই অশুভ শক্তি মাত দিয়ে যাবে। জয়িতা ভাবছে, এই জ্যামে আটকে পড়াটাও কি সেই একই কারণে? কেউ হয়ত চাইছেন না, জয়িতা এইভাবে সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে পালিয়ে যাক। পালিয়ে যাবার কথাটা মনে আসতেই জয়িতার মনে হলো, এই কথাটা তার একবারও মাথায় আসেনি যে, সে পালিয়ে যাচ্ছে। তার নিজস্ব একটা সংসার আছে। একটা আধবুড়ো স্বামী আছে। আর আছে একটা বছর তিনেকের ফুটফুটে বাচ্চা। কাউকে কিছু না-জানিয়ে এইভাবে সমস্ত কিছু ছেড়েছুঁড়ে চলে যাওয়া, এক অর্থে এটাতো পালিয়ে যাওয়াই।
হ্যান্ডব্যাগটা থেকে মোবাইলটা বার ক’রে সময়টা আরেকবার দেখে নিল জয়িতা। ঘড়িতে এখন তিনটে বেজে পঞ্চাশ।
জয়িতাকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। এখানেই চারটে বাজতে চলল!ওদিকে নিলয় হয়ত ওর দেরি দেখে ধৈর্য্য হারাচ্ছে।
এমন সময়— ”মা! মা! মা!” একটা বাচ্চামেয়ের কান্নার শব্দ জয়িতার চিন্তাজালকে মুহূর্তে ছিন্ন-ভিন্ন ক’রে দিয়ে গেল। চোখ চলে গেল পাশের সীটে। বাসে উঠেই জয়িতা লক্ষ করেছিল ওর বাঁদিকের সীটে একজন মাঝবয়েসি ভদ্রমহিলা বসে ছিলেন। ওনার কোলে বসেছিল এই বাচ্চামেয়েটি। এখন মহিলাকে আর কাছেপিঠে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। গেলেন কোথায় তিনি? সম্ভবত ওই মহিলাটিই এই বাচ্চাটির মা।
পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক বাচ্চাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, “কাঁদছো কেন, মামণি?”
বাচ্চাটি মূহুর্তের জন্য কান্না থামিয়ে লোকটির দিকে তাকালো। ভদ্রলোক উৎসাহ পেয়ে অদ্ভুত ধরনের আদুরে গলায় আবার বললেন,”কী হয়েছে খুকি? তুমি কাঁদছো কেন?” লোকটির চেহারার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নেই যা এই শিশুটিকে আকৃষ্ট করতে পারে। সারা গালে বসন্তের দাগ। রোগা ল্যাকপ্যাকে চেহারা। একটু বাদে বাদেই চোখ কচলাচ্ছে। মনে হয় লোকটির চোখে কোন সমস্যা আছে। কিন্তু গলার স্বরটি ভারি চমৎকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একজন মানুষের চেহারা আর কন্ঠস্বরে অদ্ভুত ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। একজন সুন্দর মানুষের কণ্ঠ তার চেহারার মত সুন্দর হবে তার কোন মানে নেই। চেহারা দেখে তার গলার স্বর কেমন হতে পারে আন্দাজ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার না। অবশ্য গলায় কী যায় আসে। চেহারাটাই আসল। আগে দর্শনধারী, পরে গুণ বিচারী। এক্ষেত্রেও লোকটিকে এমন সুন্দর গলায় কথা বলতে দেখে বাচ্চাটি খুব একটা প্রভাবিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। কেননা লোকটির কথা শুনে বাচ্চাটি কান্নার বেগ অনেকখানি বেড়ে গেল।
জয়িতার পাশের সীটে বসা মহিলাটি এতক্ষণ একটি কথাও বলেননি। সেই থেকে একমনে মোবাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন।। বাচ্চাটির এমন অবুঝের মত কান্নাকাটি ওনার বোধহয় ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। তিনি ঈষৎ বিরক্ত হচ্ছেন। অন্তত ওনার মুখচোখের ভাব দেখে তেমনটাই মনে হচ্ছে। তথাপি যতটা সম্ভব মোলায়েম স্বরে বললেন,”ওর মা জল আনতে নিচে গেছে। মাকে না দেখেই কান্নাকাটি শুরু করেছে। তা সে মহিলা গেছেও তো অনেক্ষণ!” তিনি হয়ত আরো কিছু বলতেন কিন্তু তার আগেই বাচ্চাটির মা বাসে উঠে এলেন। ওনার হাতে জলের বোতলটি ফাঁকা। বোধহয় অনেক চেষ্টা চালিয়েও শেষমেশ জলের জোগাড় করে উঠতে পারেননি। মিউনিসিপ্যালিটির কলগুলোতে সর্বক্ষণ জল থাকে না। এদের সময়জ্ঞান বেশ টনটনে। নির্ধারিত সময়ের আগে জল পাওয়া সম্ভব না। রাস্তার উল্টোদিকে কয়েকটা খাবারের দোকান অবশ্য দেখা যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে এক বোতল জল চাইলে কেউ না করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু চারিপাশে গাড়িঘোড়ায় এমন জট পাকিয়ে আছে, এসব টপকে সেখানে পৌঁছোনটাও বিরাট সমস্যা। যে কোন মুহুর্তে জ্যাম কেটে গিয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে বাসটা ছেড়ে দিতে পারে। যেটা ওনার জন্য একেবারেই অভিপ্রেত নয়। বাচ্চাটিকে যেহেতু বাসে একা বসিয়ে রেখে এসেছেন, সুতরাং এই পরিস্থিতিতে জল জোগাড়ের চেষ্টাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। বাচ্চাটির মাকে বাসে উঠে আসতে দেখে জয়িতার পাশে বসা সেই ভদ্রমহিলা মনে হলো যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি বেশ উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন,”ওইতো মা এসে গেছে! বাব্বাঃ, আপনাকে না দেখে মেয়ের সে কি কান্না!”
ভদ্রমহিলার কথা শুনে বাচ্চাটির মা মৃদু হাসলেন। সন্তানের মা হবার গর্বিত হাসি। হাসিটি বড় সুন্দর। কিন্তু কোন এক দুর্বোধ্য কারণে ভদ্রমহিলার হাসিটা জয়িতার সহ্য হচ্ছে না। মাকে দেখে বাচ্চাটির কান্না থেমে যাওয়ার কথা। সেটা হলো না, উল্টে মাকে দেখে বাচ্চাটির কান্না আরো বেড়ে গেল। এই কান্না সম্ভবত অভিমানের।
জয়িতার বার বার চোখ চলে যাচ্ছে ওর বাঁদিকে কয়েকহাত দূরে বসে থাকা সেই বাচ্চাটি আর তার মায়ের দিকে। বাচ্চাটি এখন মায়ের বুকে মাথা রেখে জয়িতার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের জল এখনও পুরোপুরি শুকিয়ে যায়নি। যে কারণে ওর চোখদুটো ছলছল করছে। তবে ওর চোখেমুখে আগের ঘাবড়ে যাওয়া ভাবটা আর নেই। একটু আগেও শিশুটি যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল সেটা কেটে গিয়ে তার জায়গায় একটা স্বস্তি-ভাব চলে এসেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে নিজেকে এখন বিরাট সেফ মনে করছে। সে জানে জগতের কোন দুঃখ-কষ্ট এখন তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। একটি শিশুর সবথেকে ভরসার জায়গা হলো মায়ের কোল। শিশুটির মা শিশুটিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছেন। একটু বাদে বাদে শিশুটির মাথায় কপালে চুমু খাচ্ছেন। জয়িতার মনে হলো, জগতে বোধহয় এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর হতে পারে না। কথাতেই আছে, বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। কথাটা মিথ্যে নয়।
চোখের সামনে এমন সুন্দর একটা দৃশ্য দেখলে মন ভালো হয়ে যাওয়ার কথা। জয়িতার সেটা হচ্ছে না। উল্টে মনটা ভারি হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরে অদ্ভুত একধরনের কষ্ট হচ্ছে। নিজের আত্মার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কষ্ট। মনে পড়ছে ছোট্ট বাবিনের কথা। তার নাড়ি ছেঁড়া ধন, যাকে সে একলা ঘরে বন্দি করে রেখে এসেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বাবিন ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। মাকে আশেপাশে না দেখে কান্নাকাটি শুরু করেছে। ছেলেটার মাকে ছেড়ে থাকার একদম অভ্যাস নেই। জয়িতা একটু চোখের আড়াল হলেই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। সেবার জয়িতার পক্স হয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শে বেশ ক’দিন আলাদা ঘরে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সময়টাতে বাবিনকে সামলাতে সুজয়কে যথেষ্ট পরিমাণে বেগ পেতে হয়েছিল। তখন বাবিন আধো আধো কথা বলতে শিখেছে। সারাক্ষণ শুধু “মা যাবো! মা যাবো!” করে ছেলের সে কি কান্নাকাটি। মায়ের সমস্যাটা বোঝার ক্ষমতা তখনও ওর হয়নি। কাজেই ওকে নিয়ে সুজয় মহা সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল। অন্য কেউ হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেত। সচরাচর পুরুষমানুষের ধৈর্য্য একটু কম হয়। এইধরনের চাপ সামলানোর মত মনের জোর সৃষ্টিকর্তা সম্ভবত এদের দিয়ে পাঠাননি। এই একটা জায়গায় মেয়েরা পুরুষের চেয়ে অনেক যোজন এগিয়ে। কিন্তু সুজয় অন্য ধাতুতে গড়া। তার বিরাট ধৈর্য্য। এক মুহুর্তের জন্য বাবিনকে চোখের আড়াল হতে দেয়নি।
এমনসময় বাসের খালাসি ছেলেটা বাসে উঠে এলো। এতক্ষণ ওকে দেখা যাচ্ছিল না। বোধহয় নিচে নেমে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছিল। উঠল,তবে ভেতরে এলো না। ওর যেটা জায়গা সেই বাসের দরজায় দাঁড়িয়ে বাসের গায়ে হাত দিয়ে সজোরে দু-তিনবার চাপড় মারল। যারা নিয়মিত বাসে চলাচল করেন তারা এই চাপড় মারার অর্থ জানেন। অর্থাৎ জ্যামটা বোধহয় কাটতে শুরু করেছে। এখুনি বাসটা চলতে শুরু করবে। হলও তাই। বাসটা নড়ে উঠল। বাসটা চলতে শুরু করেছে। তবে সে এগোচ্ছে ধীরে। অতি সন্তর্পণে। কোনরকমের তাড়াহুড়ো তার চলার মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বাসটাকে চলতে দেখে সবার চোখেমুখেই একধরনের স্বস্তি-ভাব চলে এসেছে। সেটাই স্বাভাবিক। জ্যামে আটকে থাকাটা খুব একটা আরামদায়ক নয়, বিরক্তিকর। বাসটা চলতে শুরু করেছে জয়িতার তো সবচেয়ে খুশি হবার কথা, অথচ তাকে খুব একটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছে না। তবে সে কি চাইছিল বাসটা আরো কিছুক্ষণ জ্যামে আটকে থাকুক? জয়িতার মনে হচ্ছে সে তার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে ক্রমাগত পিছনের দিকে টানতে শুরু করেছে। জয়িতা সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মাতালের মত টলতে টলতে বাসের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দরজার সামনে আসতেই খালাসি ছোকড়াটা তার সর্দিবসা ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল,”বউদি, এখানে দাঁড়াবেন না। কোথায় নামবেন আপনি?” ছোকড়ার কথা জয়িতার কানে ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে না। ওর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। মনে হচ্ছে জয়িতা নয়, এই মুহূর্তে ওকে চালনা করছে কোন অশরীরী। এক-দুই-তিন— সেকেন্ডের কাঁটা ক্রমশ সরে সরে যাচ্ছে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকা খালাসী ছেলেটিকে একধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে জয়িতা চলন্ত বাস থেকে লাফ দিল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। এমন আকস্মিক ধাক্কায় খালাসী ছোকড়াটি পড়ে যেতে যেতে নিজেকে কোনমতে সামলে নিল। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল,”করে কী? করে কী? গেল! গেল! গেল রে! মায়ের ভোগে গেল! কী ডেঞ্জারেস মেয়েছেলেরে বাবা! এক্ষুনি মেরে ফেলছিলো!”
আশপাশ থেকে আরও অনেকে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পারলেও একসাথে চেঁচিয়ে উঠল—’এই, এই, গেল! গেল!’
একে মেয়েমানুষ, তার উপরে এমন অনভ্যস্ত দুঃসাহসিক একটি কাজ করতে গিয়ে রাস্তার উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জয়িতা। আর একটু হলেই মিউনিসিপ্যালিটির ত্রিফলায় গোত্তা খেয়ে একটা বড়সড় অঘটন ঘটে যেতে পারত। শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু অবশ্য ঘটেনি। যদিও শরীরের অনেক অংশই ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, কিন্তু সেসব এখন ধর্তব্যের মধ্যেই আনছে না জয়িতা।
কয়েকটা মুহূর্ত, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোনদিকে না তাকিয়ে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল জয়িতা।
ঘরে ফিরছে জয়িতা। তার আদরের যাদুমণি বাবিনের কাছে ফিরে যাচ্ছে।
আমি আসছি সোনা…আমি আসছি!