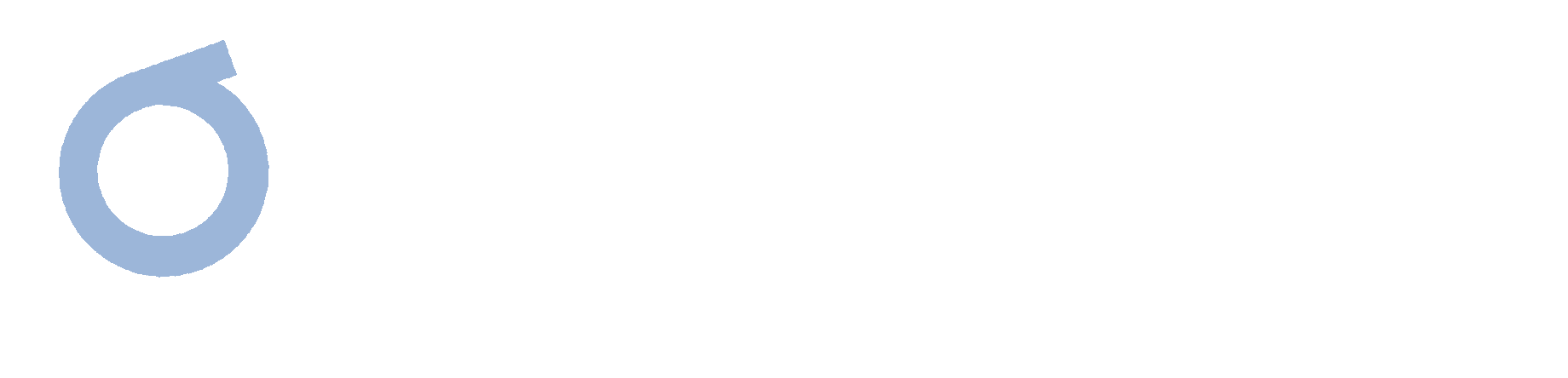সকালের দিকে বাড়ির সামনের বারান্দায় চেয়ারে বসে বিনয়ভূষণ পা দোলাচ্ছেন। তাঁর পা দোলানোর মধ্যে এক ধরনের মৃদু অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুখখানা বাংলার পাঁচ। দেখে মনে হচ্ছে, কোন একটা কারণে তিনি সক্কাল সক্কাল ভীষণ রকমের অসন্তুষ্ট। ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া থাকে। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় অ্যালার্মের কর্কশ শব্দে ওনার ঘুম ভাঙে। ওনার ঘুম খুব পাতলা। অ্যালার্ম বাজার শুরুতেই ঘুমটা ভেঙে যায়। তথাপি তিনি চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে থাকেন। ইচ্ছে করেই থাকেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেককে তার ডিউটিটা ঠিকভাবে করতে দেওয়া উচিৎ। নইলে তার কর্মদক্ষতার উপর অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। অ্যালার্মের শব্দটা পুরোপুরি একমিনিট বেজে চুপ করে গেলে চোখ খোলেন। প্রথমেই মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানান, আরো একটা দিন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কোন এক অদ্ভুত কারণে তাঁর ধারণা হয়েছে, মৃত্যুটা তাঁর দিনের বেলায় হবে না, রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে আরামের মৃত্যু হবে। যদিও এর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ওনার কাছে নেই। তবে এটা উনি মনে করেন। বিনয়ভূষণ বরাবরই একটু ধার্মিক প্রকৃতির। নিয়ম করে আহ্নিক-টাহ্নিক করেন। রাস্তায় চলার সময় শত ব্যস্ততার মধ্যেও কোন মন্দির-টন্দির সামনে পড়ে গেলে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করেন। তবে মন্দিরের সামনে রাখা প্রণামী বাক্সে কখনও পয়সা-টয়সা ফেলেন না। এ-ক্ষেত্রে ওনার যুক্তি হলো, পয়সা দেওয়াটা বড় কথা নয়। ইচ্ছে হলে দেওয়াই যায়, কিন্তু এখান থেকেই ঘুষ দেওয়ার অভ্যাসটা চালু হয়। ঘুষ দেওয়া আর নেওয়া দুটোকেই তিনি সমান অপরাধ বলে মনে করেন। গোটা চাকরি জীবনে তিনি কখনও ঘুষ খাননি। জানতেন কলিগদের অনেকেরই এই অভ্যাসটা ছিল। এমনকি অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে, গেটের দারোয়ান পর্যন্ত ঘুষ খেত। তিনি কখনও খাননি। বিণয়ভূষণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, ভগবানকে ঘুষ দেওয়া বিরাট পাপ। অতএব ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে প্রণামী বাক্সে পয়সা ফেলার অর্থ ভগবানকে প্রলোভিত করার চেষ্টা। সুতরাং এই ধরনের বেয়াদপি ভগবান কোনভাবেই বরদাস্ত করবেন না।
রোজকার নিয়মে আজও ভোরবেলায় উঠে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন বিনয়ভূষণ। কিন্তু একটা ঘটনায় ওনার মনটা সেই থেকে তেঁতো হয়ে আছে। অন্যান্য দিন বাড়ি থেকে বেড়িয়ে দক্ষিণায়ন ক্লাবের মাঠ পর্যন্ত যান। একা অবশ্য যান না, ওনার সঙ্গে আরো দু-চারজন থাকে। ক্লাব মাঠের ধার দিয়ে অনেকগুলো সিমেন্ট বাঁধানো সুন্দর বসার জায়গা আছে। সেখানে একটু বসেন, কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেন, তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসেন। আজকের ব্যপারটা একটু আলাদা। আজ উনি ইচ্ছে করেই একটু আগে আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। তিনি চাননি তাঁর সঙ্গী-সাথীরা কেউ তাঁকে দেখে ফেলুক। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা তিনি একা একা করবেন বলে ঠিক করেছেন। গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা আরো সেই কারণেই। কিন্তু এত আগেভাগে স্পটে পৌঁছেও খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেননি। তার আগেই পাখি ফুরুৎ। মেজাজটা বিগড়ে আছে সেই থেকেই।
আসলে হয়েছে কী, কিছুদিন যাবৎ ওনার গিন্নি কবিতাও নাকি মর্নিং ওয়াকে বেরোচ্ছেন। মর্নিং ওয়াকে বেরনোর মধ্যে দোষের কিছু নেই। বেরোতেই পারেন। ভোরবেলায় উঠে হাঁটাহাঁটি করাটা মোটেও খারাপ কিছু না। তার উপর কবিতার আবার বাতের ধাত আছে। বসলে উঠতে পারেন না, উঠলে বসতে পারেন না। ডাক্তার পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, শুধু গাদাগাদা ওষুধ খেলে কাজের কাজ তেমন কিছু হবে না। দিনে অন্তত ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করাটা খুবই জরুরি। বিনয়ভূষণ বহুবার স্ত্রীকে বলেছেন,”চলো কবিতা, আজ থেকে একসঙ্গে বেরোই। হাঁটাহাঁটিও হবে, আবার গল্প গুজবও হবে।” যদিও এই বয়সে দুই বুড়োবুড়ির মধ্যে কী ধরনের কথাবার্তা থাকতে পারে তা নিয়ে তিনি নিজেই যথেষ্ট সন্দিহান। তবুও সংসারের কত ছোটখাটো কথা থাকে। সবকথা ছেলে, ছেলের বৌদের সামনে বলা হয়ে ওঠে না। তাছাড়া শুধুই যে হাঁটাহাঁটি করা তা তো নয়। ভোরের নির্মল বাতাস গায়ে লাগানো শরীরের পক্ষেও খুব উপকারী। এসব কথা কবিতাকে বলে বোঝানো যাবে না। একসাথে বেরোবার কথা শুনে কবিতা এমন মুখের ভান করলেন, যেন এমন অদ্ভুত কথা তিনি এর আগে কখনও শোনেননি। মুখের উপর সটান বলেই ফেললেন,”মাথা খারাপ! আমি বেরোবো মর্নিং ওয়াকে? তাও আবার তোমার সঙ্গে?”
—”কেন, গেলে কী হবে? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে মনে হচ্ছে! তোমার বয়সী কেউ বোধহয় মর্নিং ওয়াকে বেরোয় না?”
—”যে বেরোয়, সে বেরোয়। আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, আমি যাবো বুড়োদের পালে হাওয়া লাগাতে!”
বিনয়ভূষণ আর কথা বাড়াননি। কবিতার কথাবার্তা আজকাল কেমন যেন বদলে গেছে। তার প্রতিটা কথার মধ্যেই একধরনের প্রচ্ছন্ন খোঁচা থাকে। কবিতা যে সবার সাথে এই একই ঢঙে কথা বলে তা কিন্তু নয়। বাড়ির সবার সাথেই বেশ হেসে হেসে আন্তরিকতার সাথে কথা বলে। যত ট্যারাব্যাঁকা কথা শুধু তার বেলায়। বিনয়ভূষণ এসব একদম সহ্য করতে পারেন না। বয়স বাড়লে মানুষের মন হয় শিশুর মত। যেমন অবুঝ, তেমনি অভিমানী। স্ত্রীর এ-ধরনের কথাবার্তায় বিনয়ভূষণ মনে মনে আহত হন। মুখ ফুটে কিছু বলেন না ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাগে দুঃখে ফুঁসতে থাকেন। কবিতা নিজেকে কী ভাবে কে জানে। তিনি না হয় বুড়ো হয়ে গেছেন। মানুষ চিরটাকাল একরকম থাকে না। সবারই একদিন বয়স বাড়ে, শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে বৃদ্ধ, এটাই তো জাগতিক নিয়ম। কবিতা কি সেটা বোঝে না? না, বুঝেও না-বোঝার ভান করে? কবিতার নিজেরও কি বয়স বাড়েনি? চল্লিশ বছর আগের কবিতা আর আজকের কবিতার মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। সেই ছিপছিপে গড়ন, টানটান চামড়া কি আর আছে? চেহারা-টেহারা ভারি হয়ে, গায়ের চামড়া-ফামরা কুঁচকে গিয়ে বিশ্রী লাগে দেখতে। আয়নায় নিজের চেহারা কতদিন দেখে না তাই বা কে জানে। ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই হয়ত বলা যায়। তথাপি মুখ ফুটে কিছু বলেন না বিনয়ভূষণ। কী হবে বলে? খামোখা কবিতা মনে কষ্ট পাবে। বলা-টলা ছেড়ে দিয়েছেন অনেকদিন। পছন্দ না হলেও অনেক কিছুই আজকাল মেনে নেন, মেনে নিতে হয়। সংসারে, অফিসে যে দাপট একসময় দেখিয়ে এসেছেন, রিটায়ারমেন্টের পর বাড়িতে বসে যাওয়ার পর থেকেই সংসার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বৃত্তে তাঁর ভূমিকাটা রাতারাতি অনেকখানি বদলে গেছে। এখন আর তাঁর কথা অত গুরুত্ব সহকারে শোনা হয় না। সবাই সবার নিজের মর্জিমাফিক চলতে চাইছে। বিনয়ভূষণের মাঝে মাঝে মনে হয়, ইচ্ছে করেই তাঁকে অগ্রাহ্য করার একটা প্রবণতা সকলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। চল্লিশ বছরের পুরনো গিন্নি যে গিন্নি, সেও আজকাল তাঁর কথায় তেমন পাত্তা দেন না। কথায় কথায় চিমটি কেটে কথা বলাটা তার একটা বাজে স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সবাই মিলে যুক্তি করে একসাথে তাঁর থেকে পুরনো হিসেব নিকেষ সব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে চাইছে। চাকরি থাকা অবস্থায় নিজে দেখে শুনে বড়খোকার বিয়ে দিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল ছোটটার বিয়েও নিজে পছন্দ করেই দেবেন। আজকালকার ছেলেমেয়েদের রুচির উপর খুব একটা ভরসা নেই বিনয়ভূষণের। এরা ভেতর দেখতে অভ্যস্ত নয়। বাইরের চাকচিক্যে মোহিত হয়ে অধিকাংশ সময় ঠকে যায়। পরে গোটা পরিবারকে এরজন্য পস্তাতে হয়। তো সেই ছোটখোকা যে কোনদিন বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেনি, রিটায়ারমেন্টের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে এনে ঘরে তুলল। বাপের মত-অমতের কোনরকম তোয়াক্কা না করেই। বিনয়ভূষণ কিছুই বলতে পারেননি। যদিও বলার মত সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাঁর কাছে কেউ জানতে চায়নি, এই বিষয়ে তাঁর কোন বক্তব্য আছে কী নেই। অথচ বাড়িতে রাতারাতি একজন সদস্যা বেড়ে গেল। সেইসাথে আরো একটা দায়িত্ব বাড়ল। এখন ইচ্ছে না থাকলেও হঠাৎ করে তৈরি হওয়া নতুন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দিনের পর দিন হাসি হাসি মুখ করে ‘সব কিছু ঠিক আছে’ এমন একটা হাবভাব বজায় রেখে যেতে হবে। অনেকটা জোর করে তেঁতো গেলার মত অবস্থা। ভদ্রলোক বলে কথা, একটু এদিক ওদিক হলেই মানসম্মানের একেবারে দফারফা। পরে জানতে পারলেন, ছোটবাবুর প্রেমপর্ব চলছিল অনেকদিন ধরেই। ইতিমধ্যে বারকয়েক বাড়ি বয়ে এসে হবু বৌমা হবু শাশুড়ি মায়ের সাথে দেখা টেখা করে গেছে। সেইসাথে শাশুড়ি-বৌমা সম্পর্কের ড্রেস রিহার্সালটাও বুদ্ধি করে সেরে রেখে গেছে। ছোট বৌমার বুদ্ধি আছে বটে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের শিরায় শিরায় বুদ্ধি। বিয়ের আগেই হবু শাশুড়িকে একেবারে মা-ফা ডেকে অভিভূত করে দিয়েছে। আর হবু শাশুড়ি মা’ও হবু বৌমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে একেবারে পাকা কথা দিয়ে বসে আছেন,”তুমিই আমার ছোট ছেলের বৌ হবে মা।”
বোঝ কাণ্ড! তলে তলে এতকিছু ঘটে গেছে অথচ বিনয়ভূষণ এসবের কিছুই জানেন না। শুনেছেন বয়সকালে স্ত্রী হয় স্বামীর সবথেকে কাছের মানুষ। বুড়োকালের যাবতীয় বল-ভরসা। সেই কবিতাই তাঁর অজ্ঞাতে এতবড় একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলবে, এতটা ভাবেননি তিনি। নতুন বৌমা পাকাপাকি ভাবে এ-বাড়িতে চলে আসার পর কবিতা একদিন বললেন,”সেদিন আর নেই বুঝলে? দিনকাল সব পাল্টে গেছে। কোন কিছুরই তো খবর রাখো না। এ কি তুমি আমি না-কি! তুমি যেমন আমাকে না দেখেই বাপ-মায়ের পছন্দ মত বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়েছিলে। আর আমি? বিয়ের দিন রাতে যখন বাড়িসুদ্ধ লোক ‘বর এসেছে! বর এসেছে!’ বলে হইচই শুরু করে দিল, সবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ছুটেছিলাম বর দেখতে। পরে মা, পিসি, ঠাকুমা কি বকাবকি! যেন বিরাট বড় একটা অনর্থ করে বসে আছি। আজকালকার ছেলেমেয়েরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। ওরা যেমন স্বাধীনভাবে ভাবতে পারছে, যতখানি দুঃসাহস দেখাতে পারছে, আমরা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতাম না। অভিভাবক হিসেবে আমাদের উচিৎ ওদের পছন্দ-অপছন্দকে মেনে নেওয়া।”
বিনয়ভূষণের মনে হয়েছে, কবিতা যেটা বলছে, সেটা হয়ত ঠিকই বলছে। কথার ভেতরে লজিক আছে। যুগ বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে মানুষ। সুতরাং যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে। বিনয়ভূষণ চুপচাপ সমস্তকিছু মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া ছোট বৌমা যে একেবারে খুব একটা খারাপ তা না। একটু মুখে মুখে তর্ক করে এই যা। বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে, একটু বেপরোয়া তো হবেই। কবিতার কথায়, “সবকথা অত গায়ে মাখলে চলে না।”
সেসব কিছু না। বিনয়ভূষণের আজকের অস্থিরতাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কারণে। যদিও বিষয়টা কবিতাকে নিয়েই। আসলে হয়েছে কী, গত দিন-চারেক আগে মর্নিং ওয়াক সেরে বাড়ি ফেরার পথে পরাশর বলছিলেন, তিনি নাকি কবিতাকে খুব ভোরে খালের ধারে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। তাও একদিন না, বেশ ক’দিন। পরাশরের হড়বড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস। কথা বলার সময় মুখ দিয়ে অনবরত থুথু ছেটে। বিনয়ভূষণ যেটা একদম সহ্য করতে পারেন না। শুধু পরাশর বলে নয়, এই বদভ্যাসটা অনেকের মধ্যেই আছে। এবং তারা সকলেই কথাটা একটু বেশিই বলে। পরাশর বললেন,”কী কেস বিশ্বাস দা, বৌদির সঙ্গে কিছু হয়েছে টয়েছে না-কি?”
—”মানে? তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই তো আমার মাথায় ঢুকছে না, দত্ত!”
—”না, মানে সেদিন ভোরবেলা বৌদিকে দেখলাম একা একা খালের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ভাবলাম হয়ত মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছে। আমি তো বেশ অবাকই হলাম— দেবা একদিকে দেবী আরেক দিকে!” পরাশর হাসতে হাসতেই কথাগুলো বললেন। বিনয়ভূষণ অবাক হচ্ছিলেন। পরাশর একটু বাড়তি বকে জানেন, কিন্তু নেশাভাং করে, এমন কখনও শুনেছেন বলে তো মনে পড়ে না। তিনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,”সকাল সকাল কী সব উল্টোপাল্টা বকছো বলো তো? আজকাল গাঁজা টাজায় দম দিচ্ছো না-কি হে?”
অন্য কেউ হলে বিনয়ভূষণের কথায় চটে লাল হয়ে যেত। গরম গরম দু-চারটে কথাও হয়ত শুনিয়ে দিত। কিন্তু পরাশর সেই টাইপের মানুষ না। আজ পর্যন্ত তাকে কেউ রাগ টাগ করতে দেখেনি। পরাশরের দুই ছেলেই যাকে বলে একেকটা রত্ন। দু’জনেই বিদেশে থাকে। একটা আমেরিকায়, অন্যটা জার্মানি না কোথায়। পরাশর চাকরি থেকে রিটায়ার করেছে, নাই নাই করে তাও বছর আষ্টেকের উপর তো হবেই। মিতালী সংঘ ক্লাবের একেবারে গায়েই বিরাট দো’তলা বাড়ি। অথচ অতবড় বাড়িটাতে দুটি মাত্র প্রাণী। পরাশর আর তার স্ত্রী রেণুকা। পরাশর দিলখোলা মানুষ। অধিকাংশ অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের যেটা হয়, কর্ম জীবনের ব্যস্ত সিডিউল থেকে একবার ঘরে বসে গেলে বৃদ্ধকালীন যাবতীয় সমস্যাগুলো যখন একটা একটা করে সামনে আসতে শুরু করে, নিজেকে তখন বড় অসহায় মনে হয়। সমস্ত কিছুই তখন কেমন যেন ব্যাঁকা-ব্যাঁকা ঠেকে। মনে হয় সংসারের সবাই তাঁকে ঠকাচ্ছে। তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা তাঁকে দেওয়া হচ্ছে না। কোন কিছুই ঠিকঠাক হচ্ছে না। গোটা দুনিয়া জুড়ে একটা ভয়ংকর অরাজকতা চলছে। এতদিন যেটা চোখে পড়েনি। কাউকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। এইরকম অবস্থায় কাউকে মনের কথা বলার চান্স একবার পেয়ে গেলে, রাজ্যের অভাব অভিযোগের ঝাঁপি খুলে বসে পড়ে। পরাশরের সেসব বালাই নেই। সবসময় মনে হয় আনন্দ, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে।
পরাশর তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুখে একখানা অমায়িক হাসি ঝুলিয়ে বললেন,”এখনও চেখে দেখা হয়নি বুঝলে? তোমার কথা শুনে ভাবছি এবার ওটাও একবার টেনে পরখ করার দরকার। বলা তো যায় না কবে কখন দরকার পড়ে যায়। আসলেই বৌদিকে কিন্ত আমি দেখেছি। তাও একদিন না দু’দিন। তাছাড়া ভালই তো, বৌদির এখন হাঁটাহাঁটির দরকার আছে।”
বিনয়ভূষণ আর কথা বাড়াননি। পাছে পরাশর আজেবাজে কিছু ভেবে বসে। কথার মোড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,”তারপর, তোমার ছেলেদের খবর কী? এরমধ্যে আসবে টাসবে কিছু বলেছে না-কি?”
—”না, আসার সময় কোথায়! সবাই খুব ব্যস্ত। তবে মায়ের সাথে প্রায়ই কথা টথা হয়। দেখাও হয়।”
—বিনয়ভূষণ ভ্রু কোঁচকালেন—”কথা হয় বুঝলাম। দেখা হয় মানে?”
—”সত্যি দাদা, আপনি এখনও সেই বাবরের আমলেই পড়ে আছেন। বিশ্বে এতবড় বিপ্লব ঘটে গেল— মোবাইল বিপ্লব। মানুষ এখন মোবাইল ছাড়া এক মুহুর্ত থাকতে পারছে না। মোবাইল আজ আর শুধুমাত্র দূরের মানুষজনের সাথে কথা বলার যন্ত্র না। গান, সিনেমা,গেম, তারপর ধরুন, বিভিন্ন সোশ্যাল সাইট— ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, আরো কত কী। সময় কাটানোর জন্য এর থেকে ভাল মাধ্যম আর দুটি নেই। রোজই একশোটা করে মোবাইল নতুন অবতারে মার্কেটে আসছে। তাদের ফিচারস দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। মোবাইল কোম্পানিগুলো বোধহয় নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে এসব নিয়েই দিনরাত ভাবনা চিন্তা করে চলেছে। কী করে আরো উন্নততর মোবাইল মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যায়।”
বিনয়ভূষণের মনে হলো, এই মোবাইল বিপ্লব নিয়ে পরাশর রীতিমত উচ্ছ্বসিত। মোবাইল নিয়ে তাঁর এমন লম্বা বক্তৃতা শুনলে মনে হবে, এসব বলার জন্য মোবাইল কোম্পানীগুলো তাকে ভালই টাকাপয়সা দেয়। বিনয়ভূষণ জানেন, সেসব কিছু না। পরাশরটা এমনই। সব ব্যাপারেই এর উচ্ছ্বাসটা একটু বেশিই। তিনি মুখে কিছু বললেন না, মাথা নাড়লেন। উৎসাহ পেয়ে পরাশর বললেন,”সুদূর ওয়েলিংটনে বসে ছেলে মায়ের সাথে মুখোমুখি কথাবার্তা চালাচ্ছে। এপার-ওপারের ব্যবধান কেমন এক ধাক্কায় কমিয়ে এনেছে একটা ছোট্ট যন্ত্র!”
বিনয়ভূষণ প্রথমে বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চাননি। চেয়েছিলেন গোটা বিষয়টা মাথা থেকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে। কিন্তু মানুষের মন বড় বিচিত্র। কখনও কখনও অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। আবার অনেক ছোটখাটো তুচ্ছ বিষয়ও মনের মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলে। ইচ্ছে করলেই তাকে অবহেলা করা যায় না। ঠিক সেই কারণেই বিনয়ভূষণের মনে হয়েছে, ব্যপারটা নিয়ে একটু খোঁজ খবর করা দরকার। পরাশর আর যাই হোক ফালতু কথার মানুষ না। কবিতাকে সে হয়ত সত্যি সত্যিই দেখে থাকবে। নইলে এতো জোর দিয়ে কথাটা সে বলতে পারত না। এখন বিষয়টা ক্লিয়ার করার সব থেকে সহজ উপায় হচ্ছে কবিতাকেই সরাসরি জিজ্ঞেস করা,”তুমি নাকি আজকাল মর্নিং ওয়াকে বেরোচ্ছো। কই আমাকে তো কিছু বলোনি!”
পরক্ষণেই মত পরিবর্তন করে ফেললেন। কবিতাকে এসব নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া মানেই আগ বাড়িয়ে চারটে বাজে কথা শোনা। কবিতা কি আর সেই কবিতা আছে? বললেই হয়ত বলবে,”কেন? মেয়েমানুষদের বুঝি মর্নিং ওয়াকে বেরোতে নেই? ওটা কি শুধু তোমাদের ব্যাটাছেলেদের একচেটিয়া নাকি?”
—”না, তা কেন হবে? সকালবেলা হাঁটাহাঁটি করা তো ভালো। শরীরে মনে অটোমেটিক একটা চাঙ্গাভাব চলে আসে। আমিই তো তোমাকে কতবার বলেছি মর্নিং ওয়াকে বেরোবার জন্য!”
—”তাহলে এমনভাবে বলছো যেন, বিরাট কোন অপরাধ করে ফেলেছি তোমাকে না জানিয়ে! সব কথা তোমাকে বলতে হবে এমন কোন চুক্তি আছে না-কি?”
অতএব চুপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কবিতার হুল ফোটানো কথা আর সহ্য হয় না। বিনয়ভূষণের মাঝে মধ্যে মনে হয় তাঁর সাথে এমন অদ্ভুত আচরণ কবিতা ইন্টেনশনালি করে থাকে। পুরনো কোন ঘটনার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এ বিষয়ে বাড়ির বাকী সদস্যদের সাথে যে আলোচনা করবেন তারও কোন উপায় নেই। বাড়িতে এখন দু’টো লবি কাজ করছে। একটা কবিতার, আর একটা বিনয়ভূষণের নিজের। কবিতার লবিটাই স্ট্রং। বাড়ির সবক’টা মেম্বার কবিতার টিমে। বিনয়ভূষণের লবিতে তিনি শুধু একা। পলিটিক্স যে শুধু মাঠে ময়দানে হয় তা না, সংসারের ভিতরেও পলিটিক্স চলে পুরোদমে। বাইরের পলিটিশিয়ানদের মত এখানেও যে যত দলে ভারি সংসারে তিনিই শেষ কথা বলবেন।
এসব সাত পাঁচ ভেবেই বিনয়ভূষণ এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেননি। হতে পারে পরাশর কাকে দেখতে কাকে দেখেছে। বয়স বাড়লে মানুষের চোখের পাওয়ার কমে যায়। অনেক সময় হয় না যে, দূর থেকে কাউকে দেখে মনে হয়, আরে অমুক না? কাছে গিয়ে ভুল ভাঙে। তখন বেশ লজ্জায় পড়ে যেতে হয়। এটাও হয়তো তেমন কিছু হবে। তাছাড়া কবিতাকে এসব নিয়ে কিছু বলতে গেলে আরো একটা সমস্যা আছে। কবিতা হয়ত এই নিয়ে একটা হইচই শুরু করে দিতে পারে। এমনও হতে পারে, কথাটা তাঁকে কে বলেছে, জানার জন্য চাপাচাপি শুরু করে দেবে। করবেই। তখন বিনয়ভূষণ বিপদে পড়ে যাবেন। যেহেতু তিনি নিজে চোখে দেখেননি। কিছু একটা বলে যে পাশ কাটিয়ে যাবেন সে সম্ভাবনাও একেবারে ক্ষীণ। কেননা অন্যদের মত সাজিয়ে গুছিয়ে বানিয়ে বলায় তাঁর খুব একটা সুখ্যাতি নেই। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা তাঁর একেবারেই আসে না। অতএব ওসব চিন্তা মাথা থেকে যত তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলা যায় ততই মঙ্গল। দ্বিতীয় এবং একমাত্র উপায় হলো, গোটা বিষয়টা তদন্ত করে দেখা। এবং সেটা অন্যকে দিয়ে হবে না। কাজটা তাঁকেই করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই গত কয়েকদিন ধরে গোপনে খালের ধারে যাওয়া-আসা শুরু করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বলার মত সাফল্য আসেনি। কবিতাকে খালের ধারে দেখা যায়নি। হয় তাঁর যাবার আগেই কবিতা সেখান থেকে চলে আসছে। নচেৎ বিনয়ভূষণ ঘুরে আসার পরে সে ওখানে হাজির হচ্ছে। আজকে ঠিক করেছিলেন আগেভাগে গিয়ে অনেকটা সময় অপেক্ষা করবেন। কিন্তু আজকেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ঘণ্টাখানেক খালের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে বড় বড় মশার কামড় খেয়ে শরীরে জ্বালা ধরে গেছে। তিনি যে গোপনে গোপনে নিজের স্ত্রীর উপর নজরদারি চালাচ্ছেন, মশার দল বোধহয় সেটাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখছে না।
বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে আসতে বিনয়ভূষণ ভাবলেন, মিথ্যেই তিনি পণ্ডশ্রম করছেন। আসলে বিষয়টা তেমন কিছু না। পরাশর ঠিক দেখেনি। অন্যের কথায় স্ত্রীকে অকারণে সন্দেহ করাটা মোটেও উচিৎ হয়নি। কথাটা সত্যি প্রমাণিত হলে পরিস্থিতি কী হতো সেটা অবশ্য আলাদা কথা। তবে মনে মনে তিনি বেশ স্বস্তি বোধ করলেন। সেইসাথে এটাও ঠিক করলেন কাল থেকে আর এখানে আসবেন না।
কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাইরের বারান্দায় বসে থাকার পরেও যখন কবিতা চা নিয়ে এল না, তখন কেমন যেন খটকা লাগল। প্রতিদিন মর্নিং ওয়াক সেরে বাড়ি ফিরে সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বসেন বিনয়ভূষণ। তিনি ফেরার আগেই কালু বলে ছেলেটা পেপার দিয়ে যায়। বাড়িতে কারোরই পেপার-টেপার পড়ায় তেমন আগ্রহ নেই। আগেরদিন ইন্ডিয়ার খেলা-টেলা থাকলে বড় খোকা খেলার পেজে একটু আধটু চোখ বোলায়, ব্যস্ এই পর্যন্তই। খবরের কাগজে খেলা ছাড়াও যে আরো কতরকমের খবর থাকতে পারে, সেসব নিয়ে তার অত মাথাব্যথা নেই। পেপার পড়ার মধ্যেই চা চলে আসে। অথচ আজ সেরকম কিছু হচ্ছে না। বিনয়ভূষণ মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন। কবিতা আসছে না। চা-ও আসছে না। প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে এসে বারান্দায় বসে পেপারটা হাতে নিয়ে প্রথম পাতায় হেড লাইনে চোখ আটকে গেল বিনয়ভূষণের। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার কী সব ঝামেলা শুরু হয়েছে। পড়ুয়ারা সব ন্যাপকিন ট্যাপকিন দেখিয়ে প্রতিবাদ করছে। সেই খবর আবার পেপারের ফ্রন্ট পেজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে। নিউজটা দেখেই বিনয়ভূষণের মেজাজখানা বিগড়ে গেল। এসব হচ্ছেটা কী? দেশটা যাচ্ছে কোথায়? প্রতিবাদের কী নমুনা? তাঁরাও একসময় কলেজে পড়েছেন। এ-জাতীয় আন্দোলন টান্দোলন তাঁরাও করেছেন। কিন্তু এতদূর ভাবতে পারেননি। ওভার স্মার্ট হতে গিয়ে এরা তো সব যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে! নিউজ পেপার গুলোরও খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, আজকাল হাবিজাবি খবর দিয়ে পাতা ভরাচ্ছে। বিনয়ভূষণের অভ্যাস হলো, পেপারটা তিনি শুধু পড়েন না, রীতিমত মুখস্থ ফেলেন। ছোটখাটো বা কম গুরুত্বপূর্ণ নিউজ থেকে শুরু করে, প্রতিটা বিজ্ঞাপন কোনটাই বাদ দেন না। অথচ আজ পেপার পড়তে ইচ্ছে করছে না। দু-একটা নিউজ মনোযোগ সহকারে শুরু করেও দু-তিন লাইনের বেশি এগোনো যাচ্ছে না। এমনটা কেন হচ্ছে কে জানে। বিনয়ভূষণ ভিতরে ভিতরে অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন। কিছুটা অসন্তুষ্টও মনে হচ্ছে। তিনি এতক্ষণ ধরে বারান্দায় এসে বসে আছেন, অথচ বাড়ির কারো কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। অন্যদের কথা বাদ দিলেও, কবিতাই বা চা আনতে এত দেরি করছে কেন? একবার ভাবলেন ভিতরে গিয়ে খোঁজ খবর করেন। বলা যায় না, ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে। কবিতার আবার ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে। শরীর টরীর খারাপ হলো কি-না তাই বা কে জানে। এইসব সাতপাঁচ ভাবনাচিন্তার মধ্যেই বিনয়ভূষণ দেখলেন, গেট খুলে কবিতা বাড়ির ভিতরে ঢুকছেন। বিনয়ভূষণ ভ্রু কোঁচকালেন। তার মানে কবিতা এতক্ষণ বাড়িতে ছিল না। বাইরে কোথাও বেরিয়েছিল বোধহয়। কবিতা এমনিতে খুব একটা বাইরে টাইরে বেরোয় না। আজ বেরিয়েছে। এত সকালে কোথায় যেতে পারে? বিনয়ভূষণ পেপারে নিজের মুখ আড়াল করলেন। ভান করলেন তিনি কবিতাকে দেখতে পাননি। অথচ বিনয়ভূষণকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে কবিতার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। তাঁর মুখের ভাব স্বাভাবিক। বারান্দায় উঠে বিনয়ভূষণকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে তাঁর পাশের চেয়ারটাতে ধপ করে বসে পড়লেন। বিনয়ভূষণ খবরের কাগজের আড়াল থেকেই টের পেলেন কবিতা রীতিমত হাঁপাচ্ছে। আজকের হাঁটাহাঁটিটা বোধহয় একটু বেশি হয়ে গেছে তাঁর। চেয়ারে বসেই কবিতা বললেন,”চা খেয়েছো?”
বিনয়ভূষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর খুব মনোযোগ সহকারে পড়ছেন এমন ভাবে কাগজ থেকে চোখ না সরিয়েই মাথা নাড়লেন। ওনার মাথা নাড়ানো থেকে দুটো মানে করা যায়, প্রথমটা যদি ‘হ্যাঁ’ হয়, তবে দ্বিতীয়টা ‘না’। কবিতা দ্বিতীয় মানেটা বুঝলেন। অর্থাৎ বিনয়ভূষণ এখনও চা খাননি। তিনি মনে হলো খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গলায় একরাশ বিরক্তি এনে বললেন,”এতগুলো মানুষ বাড়িতে আছে কী করতে? মানুষটা এতক্ষণ ধরে এখানে বসে আছে, অথচ কারোরই এক কাপ চা দেবার কথা মনে পড়ল না। এদের কাণ্ডজ্ঞান কবে হবে? আমি মরলে? কোনদিকে যদি একটু নজর না করেছি তো—” কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই কবিতা উঠে ভিতরে চলে গেলেন। একটু বাদে দু-কাপ চা হাতে করে পুনরায় ফিরে এলেন।— “তোমার চা—”
বিনয়ভূষণ চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে স্ত্রী’র মুখের দিকে তাকালেন। দু-কাপ চা হাতে করে কবিতা সামনে দাঁড়িয়ে। বিনয়ভূষণ খবরের কাগজটা ভাঁজ করে কোলের উপর নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা যতক্ষণে নিলেন, ততক্ষণে কবিতা আবার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়েছেন। বিনয়ভূষণ অবাক হচ্ছেন। আশ্চর্য্য! সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছে কে জানে। শেষ কবে এমন করে স্বামী-স্ত্রী সকালের চা’টা তাঁরা এইভাবে একসাথে বসে খেয়েছেন ঠিক মনে করে উঠতে পারলেন না। কবিতাকে আজ অন্যরকম লাগছে। তাঁর কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারে এক অদ্ভুত ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বামীর প্রতি তাঁকে আজ অনেক বেশি কেয়ারফুল দেখাচ্ছে। রথীন বাবুর বড় মেয়ের হাজব্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টের পর এখন কেমন আছে? বিনয়ভূষণ এ-মাসে কবে নাগাদ ডঃ সাহার কাছে চেক-আপে যাবেন? সামনের মাসে বড়-বৌমার দিদির মেয়ের বিয়েতে বাড়িসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ। সেখানে যেতে গেলেও বিরাট খরচের ব্যাপার, ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্ত কিছুই কবিতা বলে গেলেন খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই। যেন সংসারের এমন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তাঁরা হামেশাই আলাপ আলোচনা করেন। স্ত্রীর এই অদ্ভুত আচরণে বিনয়ভূষণ অবাক যেমন হচ্ছেন, আবার একেবারে ভালোও যে লাগছে না, সেটাও বলা যাচ্ছে না। তিনি হুঁ-হাঁ, আচ্ছা, ছোট ছোট শব্দে স্ত্রীর কথায় তাল দিয়ে যাচ্ছেন। এমনি আরো দু-চারটে এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন কথা বলে কবিতা ভিতরে চলে গেলেন। বিনয়ভূষণ পুনরায় খবরের কাগজটা হাতে নিয়েও নামিয়ে রাখলেন। পড়তে ইচ্ছে করছে না। তাঁকে খানিকটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। অনেকগুলো বিষয় তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রথমতঃ এত সকালে কবিতার এইভাবে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাওয়া, তারপর বেলা করে ফিরে আসা। দ্বিতীয়তঃ কবিতার এমন স্বভাববিরুদ্ধ অদ্ভুত আচরণের মানে কী? বিনয়ভূষণ বেশ ধাঁধায় পড়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। তিনি মুখ ফুটে স্ত্রীকে কিছু বলতে পারছেন না। আজকের ঘটনার পর কেন যেন তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, কোথাও যেন গণ্ডগোল একটা কিছু আছে। যেটা তিনি ধরতে পারছেন না। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। কিছুই হয়ত না। তবুও মনে হচ্ছে অনেক কিছু রহস্য এর পিছনে লুকিয়ে আছে। ভালভাবে এর তদন্ত হওয়া দরকার। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, পরাশর ভুল কিছু দেখেনি। আজ তো প্রমাণ হয়েই গেল, কবিতা সকালের দিকে সত্যি সত্যিই বাইরে বেরোচ্ছে। কতদিন ধরে বেরোচ্ছে তাই বা কে জানে। কবিতার এই বেরনো নিয়ে কোন সমস্যা নেই। ভোরবেলা হাঁটাহাঁটি করা তো ভালই। কথা সেটা নয়। কথা হলো গে, যে কোন কারণেই হোক কবিতা তাঁর এই মর্নিং ওয়াকে বেরোনোর ব্যপারটা স্বামীর থেকে আড়াল করতে চাইছেন। তিনি হয়ত চাইছেন না, তাঁর গতিবিধি কেউ টের পেয়ে যাক। অথচ বিনয়ভূষণ কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না, এটা নিয়ে এত লুকোছাপা কীসের? তবে কি এর পিছনে অন্য কোন গল্প আছে? কবিতা কি আজকাল তবে অন্য কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করছে? অন্য কেউ বলতে, বিশেষ কেউ। যার আকর্ষণ এতটাই তীব্র যে, সাতসকালে কবিতাকে বাড়ি থেকে টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। কে হতে পারে? হু ইজ হি?
ইচ্ছে করেই দু-দিন বাড়ি থেকে বের হলেন না বিনয়ভূষণ। এমনকি মর্নিং ওয়াকেও না। খুব সম্ভবত ঘরের মধ্যে থেকেই তদন্তটা তিনি শুরু করতে চাইছিলেন। বুঝে নিতে চাইছিলেন তাঁর অবর্তমানে কবিতার কাছে কেউ আসে টাসে কি-না। ফোন টোন কেউ করে কি-না। এতকিছুর পরেও বলতে গেলে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দিনকে দিন কবিতা যেন বিনয়ভূষণের কাছে রহস্যময়ী হয়ে উঠছেন। বিনয়ভূষণও নাছোড়বান্দা। কবিতাকে নিয়ে তৈরি হওয়া এই রহস্যটা সমাধানের জন্য তিনি একেবারে প্রায় উঠে পড়ে লেগেছেন। লেগে থাকলে কিছু না কিছু হবেই— খুব সম্ভবত এই জাতীয় তত্ত্বে ওনার বিরাট আস্থা আছে।
বিনয়ভূষণ তক্কে তক্কে আছেন। সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে সকলের অগোচরে কবিতা কোথায় যায়? কার সাথে দেখা করে? গোটা বিষয়টা তাঁর জানা খুব জরুরি। আবার তাড়াহুড়ো দেখাতে গিয়ে কবিতা কিছু টের পেয়ে যাক সেটাও চাইছেন না। গত দু’দিন মর্নিং ওয়াকে বেড়োননি দেখে তাঁর মর্নিং ওয়াকের সঙ্গী-সাথীরা খোঁজ খবর করে গেছেন। কী হলো? দু’দিন ধরে পাত্তা নেই! শরীর টরীর খারাপ হলো না-কি? বয়সকালে কতরকমের রোগ বালাই এসে ঝামেলা শুরু করে। কী থেকে কী হয়ে যায় তার ঠিক আছে। অবশ্য বাড়িতে এসে তাঁদের আশঙ্কা অনেকটাই দূর হয়েছে। বিনয়ভূষণকে তাঁদের যথেষ্ট ফিট বলেই মনে হয়েছে। বিনয়ভূষণও হাসি ঠাট্টা করে বন্ধুদের সাথে খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলেছেন। আজকাল তিনিও বেশ ভাল অভিনয় করতে শিখে গেছেন। বন্ধুদের তিনি জানিয়েছেন, একঘেয়েমি দূর করার জন্যই আপাতত কিছুদিন বেরোচ্ছেন না। দু-এক দিনের ভেতর আবার আগের মত বেরোবেন। বন্ধুরাও তাঁর কথা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। খোঁজ খবর নিয়ে ফেরার সময় তাঁদের হাসি হাসি মুখ দেখে তেমনটাই মনে হয়েছে বিনয়ভূষণের।
এই ক’দিনে কবিতা একবারের জন্যও বাইরে বেরোননি। তাঁর কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে কোনরকমের গোলমাল নেই। হাসছেন, কথা বলছেন, কাজের লোকের ওপর কারণে অকারণে রাগ দেখাচ্ছেন। বরাবর যেমনটা করে থাকেন অবিকল তেমনি।
বিনয়ভূষণ হতাশ হচ্ছেন। যে কারণে দু’দিন ধরে তিনি নিজেকে প্রায় ঘরবন্দি করে ফেলেছেন, এখন মনে হচ্ছে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। তাঁর বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছে, কবিতা তাঁর সঙ্গে জেনেবুঝে লুকোচুরি খেলছে। তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। বিনয়ভূষণের অবশ্য তাতে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু অভিমান হচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছে কবিতা ওনাকে ঠকাচ্ছেন। আজকাল তিনি নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছেন। সন্দেহ বলতে, শেষ বয়সে এসে কবিতা আজেবাজে কিছু একটা করে বেড়াচ্ছে, এই ধারণা তাঁর মনে ক্রমশঃ বদ্ধমূল হচ্ছে।
(২)
আজ ভোরের দিকে অ্যালার্ম বাজার আগেই বিনয়ভূষণের ঘুমটা ভেঙে গেল। এমনটা সচরাচর হয় না, আজ হলো। চোখ বুজে তারপরেও কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে একসময় উঠে বসলেন। ভাবলেন, অনেক হয়েছে, আর না। বিছানায় বসে বসেই সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ থেকে তিনি আবার আগের মত মর্নিং ওয়াকে বেরোবেন। খাট থেকে নামতে গিয়ে বিনয়ভূষণ খেয়াল করলেন, কবিতা খাটে নেই। তাঁর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। এত ভোরে উঠে কবিতা কোথায় যেতে পারে মনে মনে দ্রুত ভেবে নিলেন। তারপরেই মনে হলো, কোথায় আর যাবে? দু’দিন নাটক করে বেরোয়নি। ভেতরে ভেতরে হয়ত অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিংবা হতে পারে দু’দিন না যাওয়ায় সেই মানুষটা, যার টানে এমন নির্লজ্জের মত লুকিয়ে চুরিয়ে ভোর না হতেই ছুটে যায়, সে হয়ত এই ক’দিনের অদর্শনে অধৈর্য্য হয়ে কোন এক ফাঁকে ফোন-টোন করে থাকবে। ফোন এসে যাওয়ায় এখন তো অনেক সুবিধাই হয়েছে। যোগাযোগ রাখার জন্য বাইরে বেরোনোর দরকার নেই। ফোনেই যাবতীয় কথাবার্তা সেরে ফেলা যায়। কবিতার একটা পার্সোনাল ফোন আছে। ছোট্ট কালো রঙের ফোন। গতবছর বিবাহবার্ষিকীতে বড় খোকা মাকে গিফট করেছিল। যদিও এইসব বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন-টন্মদিন পালন করায় বিনয়ভূষণের যে খুব একটা আগ্রহ আছে তা না। বুড়ো বয়সে এইসব আদিখ্যেতার কোন মানে আছে বলে তাঁর মনে হয় না। গুচ্ছের টাকা নষ্ট। নিমন্ত্রণ করে লোক খাওয়ানো বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু না। যতসব লোক হাসানো কাজকর্ম। নতুন নতুন বিয়ের পর প্রথম প্রথম বছর তিনেক কবিতার মন রাখতে বিবাহবার্ষিকী পালন করা হয়েছে বটে, বড় খোকা হওয়ার পর থেকে টোট্যালি বন্ধ। এ নিয়ে কবিতা কম কথা শোনায়নি। বিনয়ভূষণ সেসবে একদম পাত্তা দেননি। কী হয় ওসব করে? লোকদেখানো আদিখ্যেতার তিনি ঘোর বিরোধী। এসব করে সুখী সুখী ভাব দেখানোর কোন কারণ নেই। একটা বয়স পর্যন্ত হয়ত এসব মানায়, বয়স বেড়ে যাওয়ার পর গোটা ব্যপারটাই লোক দেখানো ভড়ং ছাড়া আর কিছুই না। এতদিন হয়নি। গতবার বড় খোকার মাথায় পোকা ঢুকল। বাড়িতে অনেকদিন কোন উৎসব হয় না। লোকের বাড়িতে গিয়ে কত আর পাত পেরে খেয়ে দেয়ে চোঁয়া ঢেঁকুর তুলে জব্বর খাওয়াদাওয়া হয়েছে বলে প্রশংসা করা যায়? লোকে কী বলে? অতএব কিছু একটা করা দরকার। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটু হইহুল্লোড় করতে আপত্তি কোথায়? এমন একটা দারুণ আইডিয়া মাথা থেকে বের করায় সবাই হই হই করে খোকার বুদ্ধির প্রশংসা করলেও, বিনয়ভূষণ এর মধ্যে ছেলের কোন উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তার ছাপ দেখতে পাননি। ওনার বরং মনে হয়েছে, আমাদের ফ্যামিলি খুব সুখী ফ্যামিলি, বাপ-মায়ের প্রতি ছেলেরা যে খুব কেয়ারফুল, এটাই লোক ডেকে দেখানোর একটা অদ্ভুতুড়ে প্রচেষ্টা মাত্র। আজকালকার ছেলেমেয়েদের হাতে হঠাৎ করে বাড়তি দু’টো টাকাপয়সা চলে এলে যা হয়। যদিও এসব কথা ভাবনা-চিন্তার স্তরেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন বিনয়ভূষণ। গলা ফাটিয়ে বলার রাস্তায় আর হাঁটেননি। কেনই বা বলবেন? আর কাকেই বা বলবেন?এই বাড়িতে তাঁর জায়গাটা ঠিক কোথায়, তাঁর মতামতের গুরুত্বটাই বা কতখানি, সেটা তাঁর থেকে ভালো তো আর কেউ জানে না। সবাই অবশ্য পেটপুরে খেয়েদেয়ে নবদম্পতির— থুড়ি বুড়ো দম্পতির দীর্ঘায়ু কামনা করে দু-চারটে ভালো ভালো কথা শোনাতে বিশেষ কার্পণ্য করেনি।
বিনয়ভূষণের একবার মনে হলো, আচ্ছা, কবিতা উঠে বাথরুমে টাথরুমে যায়নি তো? কথাটা মনে হতেই চট করে একবার বাথরুমটা চেক করে এলেন। না, সেখানে কবিতা নেই। বিনয়ভূষণ আর দেরি করলেন না। দ্রুত জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে বারান্দা টপকে গেট খুলে রাস্তায় এসে পড়লেন। এখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। এখনও বেশ অন্ধকার অন্ধকার ভাব রয়েছে। কয়েক পা এগোতেই বিনয়ভূষণ টের পেলেন হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। তারপর পায়ের দিকে তাকাতেই খেয়াল করলেন তাড়াহুড়োয় জুতোজোড়া উল্টো করে পরেছেন। ডানেরটা বাঁয়ে, বাঁয়েরটা ডানে। অন্যসময় হলে নিজের এধরনের নির্বুদ্ধিতায় বিনয়ভূষণের ঠোঁটের কোণে হাসি চলে আসত। এখন অবশ্য তেমন কিছু হলো না। জুতোটা কোনরকমে ঠিক করে নিয়েই হাঁটতে আরম্ভ করলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর মনে হলো, কবিতা খুব বেশি দূর যেতে পারেনি। একটু দ্রুত পা চালালেই তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। এমন ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে বইকি। কবিতার হাঁটুর ব্যথা, সেইসাথে চেহারা খানিকটা ভারি হয়ে যাওয়ায় তাঁর গতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে গেছে। একসাথে কোথাও বেরোলে বিনয়ভূষণের আজকাল বিরক্তি ধরে যায়। তিনিও যে খুব একটা জোরে হাঁটেন তা না। তবুও এখনও তিনি যতটা জোরে হাঁটেন এই বয়সে অনেকেই তা পারেন না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সঙ্গত কারণেই মানুষের গতি কমে যায়। সেটাই স্বাভাবিক। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখা গেল বিনয়ভূষণের ধারনা খুব একটা ভুল না। ঐ তো বেশ খানিকটা দূরে কবিতা হেঁটে যাচ্ছে। অবশ্য অন্য কেউও হতে পারে। কিন্তু বিনয়ভূষণ স্থির নিশ্চিত ওটা কবিতাই। কবিতার হাঁটাচলার ভঙ্গি তাঁর অতি পরিচিত। বিনয়ভূষণের হঠাৎ মনে হলো, তিনি একটু বেশিই জোরে হাঁটছেন। এমনি করে এগোলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কবিতার কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন। অথচ তিনি চাইছেন না কবিতা টের পেয়ে যাক যে তিনি তাঁকে অনুসরণ করছেন। বিনয়ভূষণ ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি খানিকটা কমিয়ে দিলেন। আজকে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই এসেছেন— স্ত্রী’ র এই গোপন অভিসারের শেষ দেখে ছাড়বেন। কোথায় যায়? কী করে? কেননা তাঁর লজিক বলে, পাখি ধরতে নেমে শুধু ফাঁদ পাতলেই হবে না। পাখিকে ফাঁদের মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া প্রয়োজন। নইলে সমস্ত প্রচেষ্টা কোন কাজেই আসবে না। একটাই ভালো দিক কবিতা এখনও পর্যন্ত পিছন ফিরে তাকাননি। তাকালেই তিনি বিনয়ভূষণকে দেখতে পেতেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি স্বাভাবিক। কোনরকম টেনশন বা তাড়াহুড়ো তাঁর চলার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। বিনয়ভূষণের একবার মনে হলো, তিনি অযথাই বিষয়টা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তাশক্তি খরচ করে ফেলছেন। শেষে হয়ত দেখবেন ব্যপারটার মধ্যে কোন রহস্য নেই। নিছক হাঁটাহাঁটি করার উদ্দেশ্যেই কবিতা বেরিয়েছে। তাঁর সাথে বেরোতে চায় না এই যা। পরক্ষণেই ভাবলেন তাই যদি হবে তবে এত গোপনীয়তা কীসের? মুখের উপর কত কটু কথাই তো সে বলে আজকাল। বিনয়ভূষণ সেসব কথায় মনে আঘাত পান কি পান না, তা নিয়ে তাঁর খুব একটা মাথা ব্যথা আছে বলে তো মনে হয় না। উঁহু , নির্ঘাত ডালমে কুছ কালা হ্যায়। না হয়ে যায় না।
বিনয়ভূষণ দেখলেন হঠাৎ করেই কবিতা ডানদিকে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেলেন। গলিটা সরু। প্রস্থে খুব জোর পাঁচ ফুটের মত হবে। এটা আসলে খালে যাওয়ার একটা শর্টকার্ট রাস্তা। দিনের বেলাতেও এই রাস্তায় খুব বেশি লোক চলাচল করে না। বিনয়ভূষণের মনে পড়ল সেদিন পরাশর বলেছিল, কবিতাকে সে খালের ওধার থেকে এপারে আসতে দেখেছে। অর্থাৎ ভুল কিছু বলেনি সে। কিন্তু কবিতা যদি শুধু মর্নিং ওয়াক করার উদ্দেশ্যে নিয়েই বেরিয়ে থাকে তবে খালের ওধারে যাবে কেন?
খালের উপর একটা নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। এই সাঁকোই এপারে প্রীতিনগর, আর ওপারে দূর্গানগরের মধ্যে সংযোগ রক্ষার গুরুদায়িত্বটা দিনের পর যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথেই পালন করে আসছে। কবিতা বেশ সাবলীল ভাবেই সাঁকোটা পার হয়ে ওপারে চলে গেলেন। এখনও পর্যন্ত কোনরকমের অস্বাভাবিকতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা তাঁর যথেষ্ট পরিচিত। এর আগেও বেশ কয়েকবার এখানে তিনি এসেছেন। স্ত্রী’র পিছু পিছু একটা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বিনয়ভূষণ স্ত্রীকে ওয়াচে রেখেছেন। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এপারে একটা গাছের আড়াল নিয়ে। এখানে থেকে কবিতাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কবিতা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। বোধহয় কাউকে খুঁজছে। যার টানে এই সাত সকালে ছুটে আসা, যে কোন কারণেই হোক সেই ‘তিনি’ বোধহয় এখনও এসে পৌঁছতে পারেননি। খুব সম্ভবত এটাই ওঁদের মিটিং প্লেস। হঠাৎ কবিতা বুকের ভিতর হাত চালিয়ে ফোনটা বার করে আনলেন। বিনয়ভূষণ মনে মনে স্ত্রীর বুদ্ধির তারিফ না করে পারলেন না। বুদ্ধি আছে বলতেই হবে। বাইরে থেকে দেখে কোনভাবেই বোঝার উপায় নেই, মহিলার কাছে মোবাইল আছে। ফোনটা বার করে কানে ধরলেন কবিতা। অর্থাৎ কেউ ফোন করেছে। ফোনটা সম্ভবত ভাইব্রেট মোডে আছে, যে কারণে কোন শব্দ হয়নি। অথচ কবিতা ঠিক টের পেয়েছেন। বিনয়ভূষণ মনে মনে ভাবলেন, বলতেই হবে বিজ্ঞান ভারি চমৎকার একখানা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। তার আবার কতরকমের না কারুকার্য। ফোনালাপ খুব বেশি সময় ধরে চলল না। সংক্ষেপে দু’চার কথায় কাজ শেষ। ফোনে কী কথা হলো, সেটা এতটা দূর থেকে কিছুই শুনতে পেলেন না বিনয়ভূষণ। ফোনটা কান থেকে নামিয়ে আবার বুকের ভিতর চালান করে দিলেন কবিতা। ঠিক তখনই উল্টো দিক থেকে চাঁদর মুড়ি দিয়ে একজনকে আসতে দেখা গেল। বিনয়ভূষণের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। লোকটা হেঁটে আসছে খুব ধীর গতিতে। খুব সম্ভবত ওঁর ডান পায়ে কোন সমস্যা আছে। যে কারণে হাঁটার সময় ডানদিকে শরীরটা খানিকটা ঝুঁকে যাচ্ছে। চাদর মুড়ি দিয়ে থাকায় লোকটার মুখটা ঠিক স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। কাজেই আন্দাজ করা যাচ্ছে না, লোকটার বয়সটা ঠিক কত হতে পারে।
লোকটাকে আসতে দেখে কবিতা কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। দু’জনেই এখন একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দু’জনের মাঝে খুব বড়জোর হাতখানেকের ব্যবধান। বিনয়ভূষণ ঠিক শুনতে পেলেন না, কবিতার কী একটা কথায় লোকটা শরীর কাঁপিয়ে শব্দ করে হেসে উঠল। ওঁরা কথা বলছে আর মাঝে মাঝে দু’জনেই একসাথে হেসে উঠছে। কবিতা শেষ কবে এমনি করে হেসেছে, অনেক চেষ্টা করেও বিনয়ভূষণ মনে করতে পারলেন না। বোঝাই যাচ্ছে মানুষটার সান্নিধ্য কবিতা যথেষ্ট উপভোগ করছে। ওকে দারুণ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে।
বিনয়ভূষণ ধৈর্য্য হারাচ্ছেন। এভাবে চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর একটুও ভাল লাগছে না।
এই বয়সে এসে এইদিন দেখতে হবে, ভাবেননি। তাঁর নিজের উপর রাগ হচ্ছে এই ভেবে, সংসারে এতগুলো বছর একসাথে কাটিয়ে দেবার পরও কবিতাকে তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। সে কী চায়? তার মনের ইচ্ছে-অনিচ্ছাগুলোই বা কী? কিচ্ছুটি বুঝে উঠতে পারেননি। কবিতার হয়ত তাঁকে আর পছন্দ হচ্ছে না। সে হয়ত একটু অন্যভাবে জীবনটাকে উপভোগ করতে চাইছে। কিন্তু সেটা এতদিন বাদে? এসব করার এটা একটা বয়স হলো? লোকে জানতে পারলে কী ভাববে? বিদেশে অবশ্য এসব কোন ব্যাপারই না। সেখানে বয়সটা একটা সংখ্যা মাত্র। মনটাই আসল। মাঝে মাঝেই পেপারে খবর বেরোয়, নব্বই বছরের যুবক পঁচাশি যুবতীর সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কে বাঁধা পড়লেন। তাদের জীবনের শুকিয়ে যাওয়া মরুভূমিতে হঠাৎ করেই বসন্ত এসে হাজির।
এখন যদি কবিতা নতুন করে কোন সম্পর্কে বাঁধা পড়তে চায়,পড়বেই এমনটা না, যদি পড়ে। বিনয়ভূষণ হয়ত মনে বিরাট আঘাত পাবেন, কিন্তু কবিতাকে তিনি বয়সের দোহাই দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করবেন না। সে বাঁচুক। তার মত করে বাঁচুক। তিনি মেনে নেবেন। এই মেনে নেওয়ার ক্ষমতাটা এখন তাঁর প্রায় সাধনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এখন কোন কিছুতেই তিনি আর খুব বেশি বিস্মিত হন না। দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু হয় না। এক্ষেত্রে ইচ্ছা শক্তিটাই হলো গে আসল। বিনয়ভূষণ চাইছেন মনটাকে শক্ত করতে। আসন্ন ঝড়ঝাপটা কীভাবে মোকাবিলা করবেন তিনি বুঝতে পারছেন না। এই বয়সে এসে পরিস্থিতির হাতে সমস্ত কিছু সঁপে দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কী-ই বা করার থাকতে পারে? বিনয়ভূষণ শক্ত মানুষ। জীবনে বহু ঝড়ঝাপটা প্রায় একার হাতে সামলেছেন। অথচ মানসিক দিক দিয়ে তিনি আজ বেশ খানিকটা ব্যাকফুটে। তাঁর চোখদুটো কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করছে। বুকের ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হচ্ছে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট তাঁর থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ওনার চোখ-মুখ দেখাচ্ছে অনেকটা সেই ছ্যাঁকা খাওয়া প্রেমিকের মত।
ভীষণ কান্না পাচ্ছে। তিনি প্রাণপনে চেষ্টা করছেন উদগত সেই কান্নাকে আটকাতে। তবু অবাধ্য চোখ খালি ভিজে ভিজে যাচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছে সবাই একজোট হয়ে যুক্তি করে নেমেছে তাঁকে এইভাবে অপদস্থ করার জন্য।
আচ্ছা, এমন কেন হচ্ছে? তবে কি তিনি কবিতাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসেন? যে ভালবাসা হয়ত আজ পর্যন্ত সেভাবে কখনও অনুভব করা হয়নি। মনের চোরা কুঠুরিতে কোথাও হয়ত সেই ভালবাসা আগে থেকেই আত্মগোপন করে ছিল। তিনি তা টের পাননি। যুবক অবস্থায় কখনও প্রেম করেননি বিনয়ভূষণ। করেননি মানে করার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কলেজ জীবনে দু-একজন মেয়েকে মনে যে একেবারে মনে ধরেনি তা না, কিন্তু সেটা একতরফা ভাললাগা ছাড়া আর কিছু না। মন দেয়া-নেয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়নি। কলেজ থেকে বেরিয়ে খুব বেশিদিন বাড়িতে বসে থাকতে হয়নি বিনয়ভূষণকে। চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন। চাকরির হওয়ার ঠিক একবছরের মাথায় কবিতার সাথে বিয়ে। তারপর ছেলেপুলে সংসার এসব নিয়ে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, আলাদা করে প্রেম ভালবাসা নিয়ে ভাবার অবকাশ হয়নি কখনও। তাঁর ধারণা ছিল, দেখেশুনে বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসা হয় না। একটা টান হয়ত তৈরি হয়, কিন্তু সেটা দু’টো মানুষ দীর্ঘদিন একসাথে থাকার ফলে যেমনটা হয়, অনেকটা সেরকম। এখন মনে হচ্ছে বিষয়টা পুরোপুরি ঠিক নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও প্রেম-ভালবাসা হয়। সংসার জীবনের বিবিধ জটিলতায় সেটা সবসময় টের পাওয়া যায় না এই যা। অর্থাৎ বিনয়ভূষণ কবিতাকে ভালবাসেন। হয়ত একটু বেশিই বাসেন। কিন্তু কবিতা যে কথায় কথায় বলে, তাঁর মত শুকনো খটখটে টাইপের মানুষ এই জগতে আর দু’টো নেই। তাই যদি হবে, তবে সেই শুকনো বুকে স্ত্রীর প্রতি এত ভালবাসা আসছে কোত্থেকে? না, কবিতা ঠিক বলে না।
ওঁরা কথা বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওঁরা হাঁটছে। হাঁটার মধ্যে কোন রকমের তাড়াহুড়ো নেই। শুধু সময় নষ্ট করার জন্যই হাঁটাহাঁটি।
এখনও পর্যন্ত লোকটার মুখ দেখার সুযোগ হয়নি বিনয়ভূষণের। লোকটা একবারের জন্যও চাদরের ঘোমটা সরায়নি। বিনয়ভূষণের ভাবলেন, আচ্ছা, লোকটা কি তাঁর চেয়েও দেখতে শুনতে ভালো? মানে, কবিতা ওই হতচ্ছাড়াটার মধ্যে এমন কি দেখতে পেয়েছে, যা তাঁর মধ্যে নেই? মেয়েদের চয়েস বোঝা মুশকিল। কী যে ওদের পছন্দ, আর কী যে অপছন্দ, সেটা বোধহয় ওরা নিজেরাও ভালো করে জানে না। বিনয়ভূষণের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আচ্ছা, তিনি কি ওই অজ্ঞাত পরিচয় লোকটাকে হিংসে করছেন? সেটাও বলা যাচ্ছে না। কেননা, নিজের স্ত্রী অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে এইভাবে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করছে তাঁর তো ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠার কথা। তা হচ্ছে না, বদলে ওদের প্রতি একধরনের সহানুভূতি জাগছে। অনেকদিন আগে তিনি একটা সিনেমা দেখেছিলেন। যেখানে দেখানো হচ্ছিল, এক ভদ্রলোক বিয়ের কিছুদিন পর জানতে পারলেন, তাঁর সাথে বিয়ে হবার আগে স্ত্রী’র অন্য একজনেরর সাথে ভাব-ভালবাসা ছিল। বাবা-মায়ের চাপে পড়ে তাঁদের পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করতে তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন। সব জানার পর স্বামী ভদ্রলোক মনে মনে খুব দুঃখ পেলেও, তিনি মনস্থির করলেন যেমন করেই হোক স্ত্রীকে তাঁর ভালোবাসার মানুষটির সাথে মিলিয়ে দেবেন। সিনেমার শেষটা কী হয়েছিল এতদিন বাদে আর ঠিক মনে নেই। তবে সেই স্বামী ভদ্রলোকটির মহানুভবতা বিনয়ভূষণকে যথেষ্ট অভিভূত করেছিল। সেদিন একবারের জন্যও মনে হয়নি তাঁকেও একদিন এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে। এখন তাঁর কী করা উচিৎ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কীর্তিকলাপ দেখবেন? না-কি চুপচাপ যেমন এসেছিলেন তেমনি বাড়ি ফিরে যাবেন? কোন কিছুই বিনয়ভূষণ বুঝে উঠতে পারছেন না। বিনয়ভূষণ উপরের দিকে তাকালেন। মাথার উপরে সীমাহীন আকাশ। আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের উদারতার ভাব চলে আসে। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো, হঠাৎ করেই তাঁর মধ্যে একধরনের উদারতার ভাব চলে এসেছে। কোনরকমের সমস্যা ছাড়াই জগতের যাবতীয় আঘাত, তিনি হাসি মুখে মেনে নিতে পারবেন। এইসমস্ত হাবিজাবি চিন্তা-ভাবনা করতে করতে বিনয়ভূষণ দেখতে পেলেন কবিতা ফিরে আসছেন। সঙ্গে সেই লোকটাও। কবিতাকে বোধহয় খানিকটা পথ এগিয়ে দিতে চায়।
বিনয়ভূষণ আরো কিছুটা গাছের আড়ালে সরে এলেন। তিনি চাইছেন না ওঁরা তাঁকে দেখে ফেলুক। ওনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, কোনভাবে যদি ওনার অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে কবিতা বা তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক নন, বিনয়ভূষণ নিজেই বিরাট লজ্জায় পড়ে যাবেন।
তাকাবেন না ভেবেও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আসা লোকটাকে এক ঝলক দেখার লোভ বিনয়ভূষণ সামলাতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো, কে তাঁর চল্লিশ বছরের বিয়ে করা বৌয়ের মন হরণ করল, তাকে একবার চোখের দেখা দেখে নিতে ক্ষতি কোথায়?
লোকটার মাথায় চাদরের ঘোমটা এখন আর নেই। এতক্ষণে তাঁর মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয়ভূষণ মনে হলো, ভীষণ রকমের চমকে উঠলেন। এর থেকে বড় চমক এই মুহূর্তে তাঁর জন্য আর কিছু হতে পারে না। কবিতার সঙ্গে এ কাকে দেখছেন তিনি? একে যে তিনি চেনেন। শুধু চেনেন বললে ভুল হবে, খুব ভালভাবেই চেনেন। এটা তো জ্যোতি! কবিতার ভাই জ্যোতির্ময়— তাঁর একমাত্র শ্যালক। হা ভগবান! বিনয়ভূষণ নিজের মাথায় একটা আলতো করে চাটি মারলেন। ছিঃ! এতক্ষণ ধরে কী সব আজেবাজে কথা চিন্তা করে মাথা খারাপ করছিলেন। অযথাই কবিতাকে বিশ্রী সন্দেহ করছিলেন। জ্যোতি! সেই জ্যোতি! কতদিন বাদে দেখলেন ওকে। ইস্, কী চেহারা হয়েছে ওর? এত কাছ থেকে না দেখলে ওকে তো চিনতেই পারতেন না। অথচ একটা সময় কী চেহারাখানাই না ছিল ওর। বিনয়ভূষণ ঠাট্টা করে বলতেন, “বুঝলে জ্যোতি, তোমার কিন্তু সিনেমা লাইনে ট্রাই করা উচিত। তোমার যা চেহারা, তাতে ফিল্মের হিরো টিরো হয়ে যেতে পারো।”
সেইসব দিনের কথা বিনয়ভূষণের সব মনে পড়ে যাচ্ছে। কবিতার বাপের বাড়ি মাঝদিয়ায়। বিনয়ভূষণের বাবা ফণিভূষণ দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে সেই মেয়ের খুড়তুতো বোন কবিতাকে পছন্দ করে বসলেন। শুধু পছন্দই নয়, একেবারে পাকা কথাবার্তা সেরে এলেন, কবিতাকেই তিনি নিজের ছেলের বৌ করে ঘরে তুলবেন। সে কি আজকের কথা? বিনয়ভূষণ তখন সদ্য সদ্য চাকরিতে ঢুকেছেন। বিয়ের আগে একবারের জন্যও কবিতাকে দেখতে যাওয়ার কথা মাথাতেই আসেনি তাঁর। মা, আর দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব অবশ্য গিয়েছিল মেয়ে দেখতে। তিনি যাননি। একেবারে শুভ দৃষ্টির সময় কবিতার মুখ দেখেছিলেন। তার আগে অবশ্য কবিতার একটা ফটো দেখেছিলেন। সেইসময় তাঁর মনে হয়েছিল, ছবি সবসময় একজন মানুষের সঠিক চিত্র তুলে ধরে না। কেননা, ছবিতে যা দেখেছিলেন, কবিতা তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।
কবিতারা পিঠোপিঠি দুই ভাইবোন। সময়ের মাপকাঠিতে কবিতাই বড়। বিনয়ভূষণের বড় ছেলে আবীরের যেবার জন্ম হলো, সেবার বছরখানেকের মত দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে এসে ছিলেন জ্যোতির্ময়। জ্যোতির্ময় বরাবরই একটু অলস প্রকৃতির। কাজকর্মের প্রতি তাঁর চরম অনীহা। কবিতার বাবা ছেলেকে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন এখানে কিছুদিন থাকলে যদি ছেলের মতি গতি ফেরে।
সেবার বিনয়ভূষণ দোতলায় হাত দিয়েছেন। প্রতিদিনই প্রায় কমবেশি মিস্ত্রী, লেবার লেগেই আছে। বিল্ডার্সকে পেমেন্ট করবেন বলে আগের দিনই হাজার বিশেক টাকা ব্যাংক থেকে তুলে এনে কবিতাকে দিয়েছিলেন আলমারিতে তুলে রাখার জন্য। পরদিন যথাসময়ে বিনয়ভূষণ টাকাটা চাইলেন। কবিতা তড়িঘড়ি আলমারি খুলে টাকা বার করতে গিয়ে দেখলেন, চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে। আলমারিতে টাকা নেই। সারা আলমারি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন লাভ হলো না। নেই তো নেই, কোথাও নেই। সব শুনে বিনয়ভূষণের ভীষণ রাগ হলো। টাকা খোয়া যাওয়ার যন্ত্রণা তো আছেই, তারপর বিল্ডার্সকে কথা দেওয়া আছে। কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারলে বেইজ্জত হতে হয়। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে একগাদা বাইরের লোকজনের সামনে স্ত্রীকে যা নয় তাই পাঁচ কথা শুনিয়ে দিলেন। রাগ করে দিন চারেক বাড়িতে এলেন না। রাগ পড়লে যখন বাড়ি ফিরলেন, কবিতা তখন অসুস্থ হয়ে বিছানা নিয়েছেন। আরো জানলেন, জ্যোতির্ময় বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। জানতে পারলেন, টাকাটা আর কেউ নয়, জ্যোতির্ময়ই সরিয়েছিল। টাকাটা নেওয়ার সময় তার একবারও মনে হয়নি, তার এই কৃতকর্মের জন্য দিদি-জামাইবাবুর মধ্যে তুমুল ঝামেলা লেগে যেতে পারে। কবিতা যখন আলমারিতে টাকাগুলো তুলে রাখছিলেন জ্যোতির্ময় তখন কাছাকাছিই ছিলেন। অতগুলো টাকা একসঙ্গে দেখে লোভ সামলাতে পারেননি। বরাবরই দিদির উপর মায়াটা তাঁর একটু বেশিই। কবিতাও ভাই বলতে অজ্ঞান। শুধুমাত্র তাঁর একটা ভুলের জন্য দিদির সংসারে অশান্তি শুরু হয়ে যাবে, এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। যাওয়ার আগে দিদি-জামাইবাবুকে উদ্দেশ্য করে একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। সে চিঠির সারমর্ম এই— টাকা-কাণ্ডে দিদির কোন দোষ নেই। তার জন্যই যতকিছু গণ্ডগোল। এই কারণে তিনি ভীষণভাবে লজ্জিত। এই পোড়া মুখ আর কখনও তিনি দেখাতে চান না। যদিও ক্ষমার অযোগ্য, তবুও পারলে যেন তাকে ক্ষমা করা হয়। আর টাকাটা যথাস্থানে রাখা আছে। সবটা অবশ্য রাখা গেল না। কেননা কিছু টাকা তিনি ইতিমধ্যেই খরচ করে ফেলেছেন। পরে যদি কখনও সময় সুযোগ আসে টাকাটা সুদে আসলে ফেরৎ দেবার চেষ্টা করবেন। চিঠি পড়ে বিনয়ভূষণ অবশ্য খুব বেশি অবাক হননি। কেননা প্রথম থেকেই তাঁর সন্দেহ হচ্ছিল, এই কাজটি জ্যোতির্ময় ছাড়া কেউ করেনি। তাঁর সন্দেহটা যে অমূলক ছিল না, এই চিঠিই তার প্রমাণ। বিনয়ভূষণ স্ত্রীর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছিলেন। আর বুঝতে পারছিলেন বলেই, এ-নিয়ে আর কথা বাড়াননি। বিনয়ভূষণের শ্বশুর মশাই ছেলের এই অপকর্মের দরুণ মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন। সেইসাথে ভীষণ লজ্জিত। সেই অপরিসীম লজ্জা এড়াতেই হয়ত ভদ্রলোক জীবনে আর মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িমুখো হননি। বিনয়ভূষণ এসব নিয়ে স্ত্রীকে কিছু বলেননি। কিন্তু কবিতাও আর কোনদিন বাপের বাড়ি যাবার নামও মুখে আনেননি। এমনকি বাবার মৃত্যুর খবর পেয়েও ও-বাড়িতে যাওয়ার ব্যপারে আগ্রহ দেখাননি। মেয়ের কর্তব্য হিসেবে এ-বাড়িতেই তেরাত্রি পালন করে নিজের দায়িত্ব সেরেছেন। তারপর মাঝের এতগুলো বছর— নেই নেই করে তাও বছর তিরিশেক তো হবেই। বেশি বই কম না। কোথা দিয়ে পার হয়ে গেছে খেয়ালই নেই। বিনয়ভূষণও কথাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন বিনয়ভূষণ বিশ্বাসের স্ত্রী, দুই সন্তানের মা হবার আগেও কবিতা কারো মেয়ে, কারো বোন। শিকড়ের মায়া তাঁরও থাকতে পারে। বিনয়ভূষণের ভাই-বোনেরা কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোন চেষ্টাই করেননা। কেন করেন না, সেটা বড় কথা নয়। তাঁরা ভুলে গেলেও তিনি কি তাঁদের একমুহুর্তের জন্যও ভুলতে পেরেছেন? কে জানে তাঁরাও হয়ত ভোলেননি। ভুলে থাকার ভান করে আছে মাত্র। রক্তের সম্পর্ককে কি এত সহজে অস্বীকার করা যায়? তেমনি করে কবিতাও পারেনি বাপের বাড়ির লোকেদের কথা, একমাত্র ভাইয়ের কথা ভুলতে। শুধুমাত্র স্বামীর অহংকারকে জিতিয়ে দিতে তার এই আত্মত্যাগ। বলতেই হবে কবিতা এতগুলো বছর বিরাট ধৈর্য্য দেখিয়ে এসেছে।
আজ এতদিন বাদে জ্যোতিকে দেখে বিনয়ভূষণের এতটুকু রাগ বা বিরক্তি কোনটাই হচ্ছে না। বরং তাঁর ভালই লাগছে। এখন মনে হচ্ছে একটা বড় ধরনের ভুল তিনি করে বসে আছেন। পুরনো ঝুটঝামেলা মনে পুষে না রেখে, দু’টি পরিবারের মধ্যে তুচ্ছ কারণে তৈরি হওয়া দূরত্বটাকে কমিয়ে আনার ব্যাপারে তাঁর আরো আগেই উদ্যোগী হওয়া উচিৎ ছিল। সেটা তিনি করেননি। সমস্যাটা শুধু স্ত্রীর সমস্যা ভেবে যথেষ্ট পরিমাণে অবহেলাই দেখিয়ে এসেছেন। এখন মনে হচ্ছে, সেটা একেবারেই ঠিক হয়নি। আজ এই মুহুর্তে দাঁড়িয়ে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি দূরে সরিয়ে দুই বাড়ির মানুষগুলোকে যত তাড়াতাড়ি কাছে আনার ব্যবস্থা করা যায়, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবেন।
বিনয়ভূষণ দেখতে পেলেন কবিতা আর জ্যোতির্ময় পাশাপাশি তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। গাছের আড়ালে থাকায় ওঁরা তাঁকে দেখতে পাননি। বিনয়ভূষণ একবার ভাবলেন ওদের সামনে হঠাৎ করে আত্মপ্রকাশ করে দু’জনকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেন। এমনটা করলে ব্যপারটা কেমন হয়? পরক্ষণেই মত বদলালেন। না, থাক, তার কোন দরকার নেই। কিছু কিছু ঘটনা অপ্রকাশিত থাকাই ভালো। তাতে করে সম্পর্কগুলোর মাধূর্য বাড়ে। তাঁর কথা শুনে না হোক, অন্তত ভাইয়ের টানে কবিতা তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস ভেঙে আজকাল মর্নিং ওয়াকে বেরোচ্ছে। এটাই কম কী? একটা বয়সের পর নিয়মিত মর্নিং ওয়াকে বেরনো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। শরীর, মন দু’টোই বেশ চাঙ্গা থাকে।
-: সমাপ্ত :-